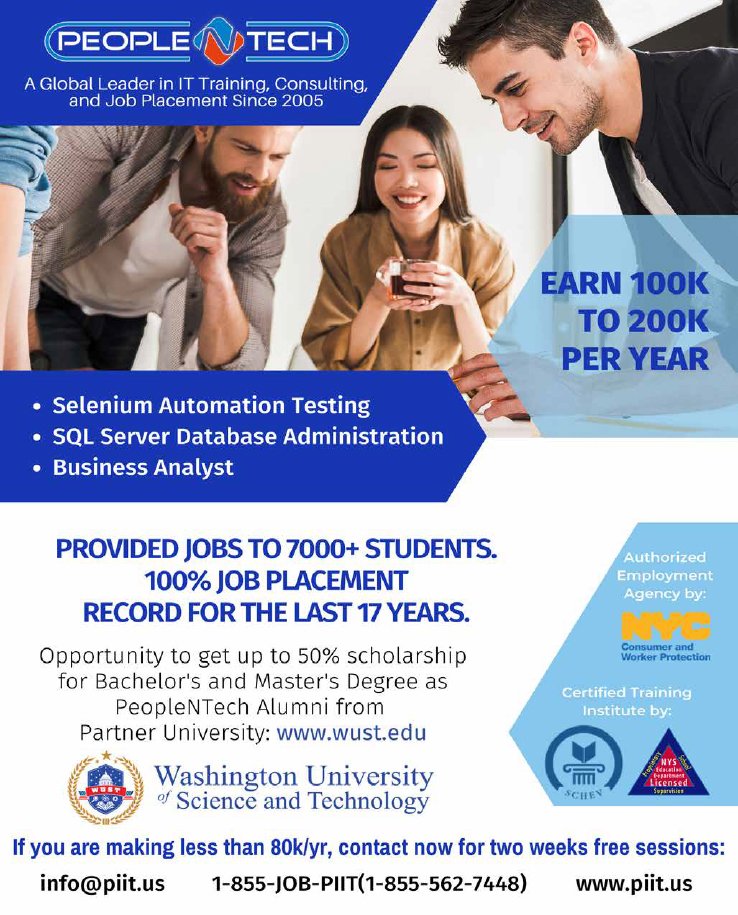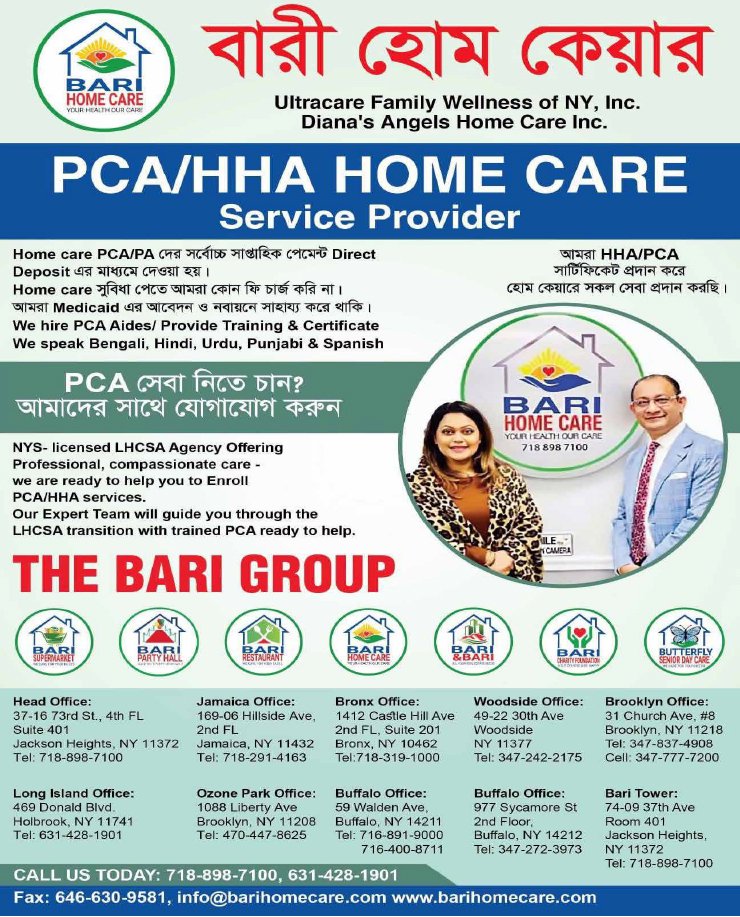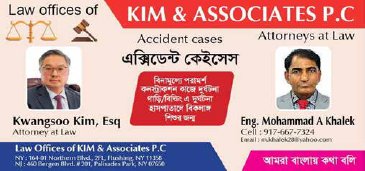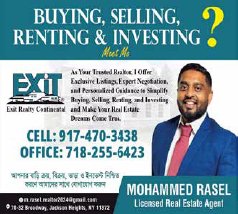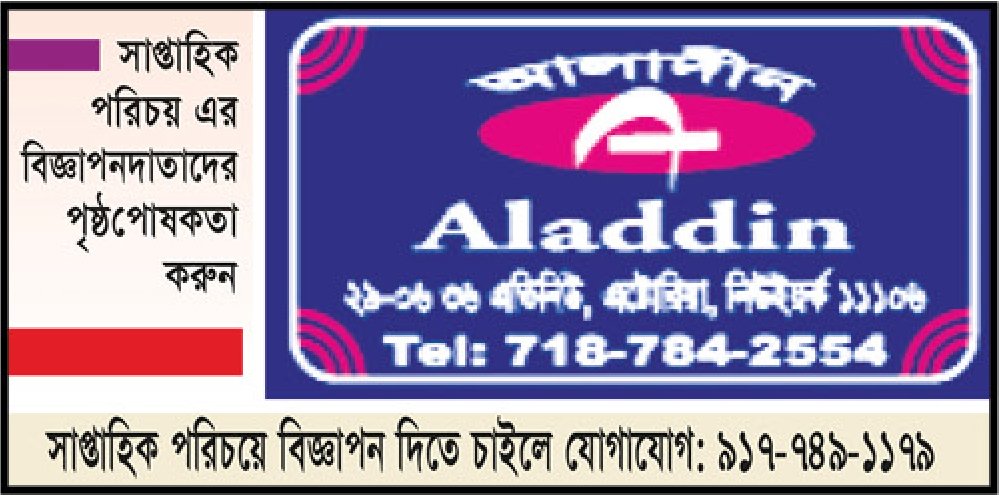

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামটা জাতীয়তাবাদীরাই শুরু করেন। ১৮৫৭ সালে কোম্পানির অধীনস্ত সিপাইরা যে অভ্যুত্থানটি ঘটান, সেটাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা হয়। এই বলাতে কোনো অতিশয়োক্তি নেই। সংগ্রামটা ছিল ব্রিটিশের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদীদের। এটি দমন করতে শাসকদের আরাম সত্যি সত্যি হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল, ওই রকম আরেকটি অভ্যুত্থান যদি ঘটে তাহলে সেটিকে দমন করা সম্ভব হবে না। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন ও কার্যকর রণনীতি– ভাগ করো এবং শাসন করো প্রয়োগ জোরদার করে। তাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল এমন একটি তাঁবেদার শ্রেণি তৈরি করা, যেটি তার নিজের স্বার্থেই কেবল যে শাসকদের সেবা করবে, তা-ই নয়; অভ্যুত্থানের যে কোনো চেষ্টাকে দমন করতেও সহায়ক হবে।
সিপাই অভ্যুত্থানে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদের সমস্যা দেখা দেয়নি। আর ওই ঐক্যেই ছিল শাসকদের বিশেষ উদ্বেগ। তাই প্রথম থেকেই তারা ঠিক করে যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ বাড়াবে এবং পারলে সংঘাত সৃষ্টি করবে। প্রথম জনশুমারিতে তাই দুই সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হলো। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে কাল-বিভাজন সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখিয়েই করা হলো। তাদের ওই যুগ-বিভাজনে প্রথমে ছিল হিন্দু যুগ, তারপর এলো মুসলমানরা। তারা হিন্দুদের দমন করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল; এর পরে এলো ইংরেজ। ইতিহাসকে এভাবে দেখিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে– মুসলমানরা এসেছিল আপদ হিসেবে, যাদের হাত থেকে দয়ালু ইংরেজরা এসে হিন্দুদের রক্ষা করেছে। নিজেদের শাসনকালকে কিন্তু তারা খ্রিষ্টান যুগ বলেনি। বলেছে আধুনিক যুগ। আর নতুন যে শ্রেণি তৈরিতে তারা হাত লাগিয়েছিল, সেই শ্রেণির মুখপাত্ররাও ইংরেজদের লুণ্ঠনকারী হিসেবে না; দেখেছে মুক্তিদাতা হিসেবেই। এই নতুন শ্রেণি হিসাব করে দেখেছে, ইংরেজরা তাদের কেবল যে মোগলদের শাসন থেকে বাঁচিয়েছে, তাই নয়; বাঁচিয়েছে মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকেও। রেনেসাঁর আলোয় ভাসিয়ে দিয়েছে ভারতভূমিকে; বিশেষ করে বঙ্গভূমিকে, যেখানে বিদেশি ওই ত্রাণকর্তারা প্রথমে দখলদারিত্ব কায়েম করে।
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যাতে সভা বসিয়ে তাদের আবেদন-নিবেদন অভাব-অভিযোগ বড়কর্তাদের কর্ণগোচর করে নিজেদের অসন্তোষ থেকে ভারমুক্তির ক্ষণিক আরাম পেতে পারে, সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কাজে। পরে যখন দেখল, তাতেও কুলাচ্ছে না; শিক্ষিতদের একাংশ উশখুশ করেছে, তখন সাম্প্রদায়িকতাকে আরও সামনে নিয়ে আসবার অভিসন্ধিতে উঠতি মুসলমানদের উৎসাহিত করল সারা-ভারত মুসলিম লীগ নামে কংগ্রেসের পাল্টা একটি দল গড়তে। বাংলাই যেহেতু হয়ে উঠেছিল অসন্তোষের ডিপো, তাই প্রশাসনিক সুবিধা হবে– এই অজুহাত দাঁড় করিয়ে বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্যোগও নিল। শিক্ষা, চাকরি, পেশায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায় তখন অগ্রসর। কারণ মুসলিম শাসনামলেও ব্যবসায় তো বটেই, দাপ্তরিক কাজেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন নিলামে জমিদারি কিনে তারা জমিদার হয়ে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে মুসলমানরা যেহেতু রাজ্যহারা; তাই তাদের ভেতর হতাশা ও অভিমান ছিল। দখলদারদের ভাষা শিখতে তারা বিলম্ব করল। এসব কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল ইংরেজরা চলে যাবে না; থাকার জন্যই এসেছে, তখন চলমান ওই শকটে সওয়ার হবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগে পূর্ববঙ্গবাসী, বিশেষ করে ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের কিছুটা সুবিধা হবে মনে করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওই বিভাজনে আপত্তি ওঠেনি, বরং সম্মতিই দেখা গেছে। কিন্তু কলকাতাবাসী জমিদার ও পেশাজীবীরা দেখল পূর্ববঙ্গে তাদের যে জমিদারি আছে এবং সেখান থেকে যে খাজনা, মক্কেল, রোগী, শিক্ষার্থীরা আসে সেসবের অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রমাদ গুনে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলল। নেতৃত্ব যেহেতু ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে, তাই আন্দোলনে হিন্দুত্বের ছাপ পড়া ছিল স্বাভাবিক। এর ফলে দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে সহায়তা পেল।
ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের নতুন রাজনৈতিক আরেকটা চাল চালল। অল্পসংখ্যক লোককে ভোটাধিকার দিয়ে (শুরুতে ছিল শতকরা দুজন) ভান করল ছাড় দেবার। কিন্তু ভেতরে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিমন্ত করবার জন্য ব্যবস্থা নিল পৃথক নির্বাচনের– যে ব্যবস্থায় হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দু প্রার্থীদের; মুসলমানরা দেবে মুসলমান প্রার্থীদের। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় ভোটাধিকারপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছিল শতকরা ১২-তে; কিন্তু পৃথক নির্বাচন পূর্ববৎ বহাল ছিল।
স্বাধীনতাদানের নামে সাতচল্লিশে দেশকে দুই টুকরো করা হলো এবং রাষ্ট্রক্ষমতা ধরিয়ে দেওয়া হলো দুদিকের দুই জাতীয়তাবাদী দলের হাতে। বাংলা ও পাঞ্জাব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র। বিভাজনের খড়্গ গিয়ে পড়ল ওই দুই প্রদেশের ঘাড়ে। তাতে উভয় প্রদেশের যে ক্ষতি ঘটল, তা নানান দিক দিয়েই অপূরণীয়। বাংলার জন্য ১৭৫৭-তে ঘটেছিল প্রথম ট্র্যাজেডি; ১৯৪৭-এ ঘটল দ্বিতীয়টি; ইংরেজের আগমন ও নির্গমন সূত্রে।
স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীরাই প্রথম ও প্রধান ছিলেন। তবে জাতীয়তাবাদীরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেননি; সেটা পাবেন বলে আশাও করেননি। কার্যত জাতীয়তাবাদকে তারা সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করেছিলেন। ওই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিল ব্রিটিশের। যে-লড়াইটা হবার কথা ছিল স্বাধীনতার, সেটি পরিণত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে; নজরুলের কবিতার ভাষায় টিকি ও দাড়ির মারাত্মক টানাটানিতে। স্বাধীনতা জনগণকে মুক্তি দিল না, বরং আবদ্ধ করল নতুন এক জালে।
সমাজতন্ত্রীরা কেবল জাতিগত স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন জাতীয় স্বাধীনতাকে নিয়ে যাবেন জনগণের মুক্তির অভিমুখে। কিন্তু তারা তো শক্তিশালী ছিলেন না। এর প্রথম কারণ রাজনীতিতে তারা এসেছেন জাতীয়তাবাদীদের পরে; ১৯১৭-এর সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। আবার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্টরা আক্রমণের শিকার হন; যেমন শাসকদের তেমনি শাসকবিরোধী জাতীয়তাবাদীদেরও।
ব্রিটিশ শাসকরা ভয় পেয়েছে– কমিউনিস্টরা ১৮৫৭-এর আগুনকে পুনরায় প্রজ্বলিত করবে এবং সে-ঘটনায় মধ্যবিত্তের একাংশের সঙ্গে মিলিত হবে মেহনতি মানুষ। পরিণতিতে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ফরাসি বিপ্লবের মতোই ‘ভয়াবহ’ এক সামাজিক বিপ্লবের। জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন উঠতি বুর্জোয়া ও ধনী ভূস্বামী; বিপ্লবের আতঙ্কে কম্পিত তারাও হয়েছেন। ব্রিটিশ চেয়েছে বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী পার্টিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে; ওই কাজে তারা দমন-পীড়নের সদর ও গোপন সকল রাস্তাই ব্যবহার করেছে। এর পাশাপাশি ছিল ভাববাদিতার চর্চা। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন দুজন– মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাদের ভেতর বিস্তর পার্থক্য ছিল, কিন্তু ঐক্য ছিল এক জায়গায়, সেটা হলো ভাববাদিতাকে উৎসাহ প্রদান। তৎকালীন চিন্তাবিদদের কেউই যথার্থ সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন না। কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যেও ছিল বিভ্রান্তি; ছিল জ্ঞানচর্চার সুযোগের অভাব এবং ছিল বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ফলপ্রসূ বৈপ্লবিক রণকৌশল গ্রহণের ব্যাপারে অপারগতা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে