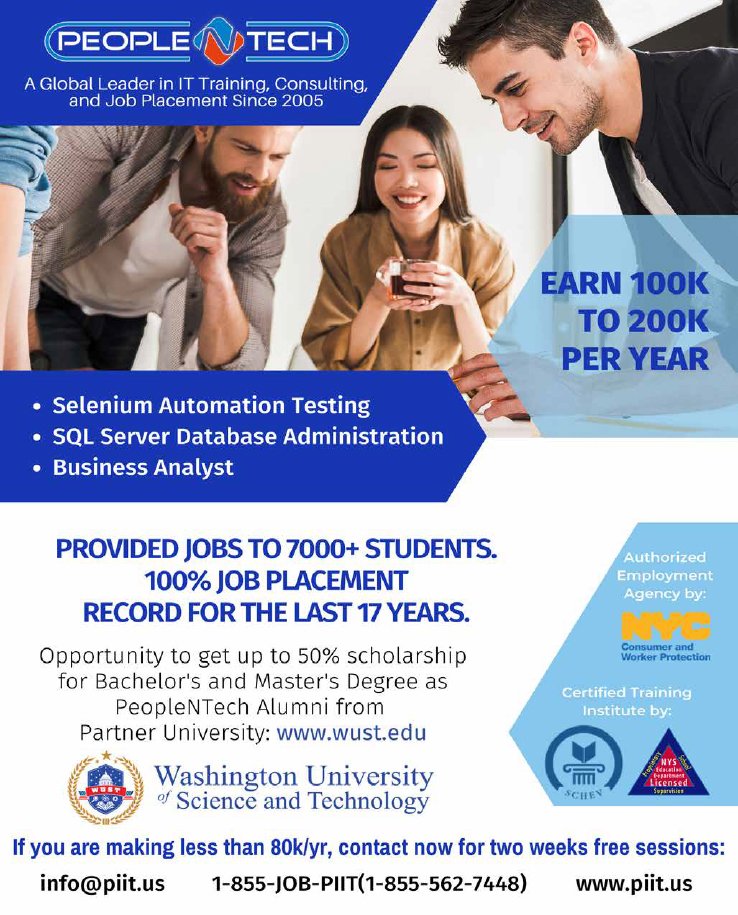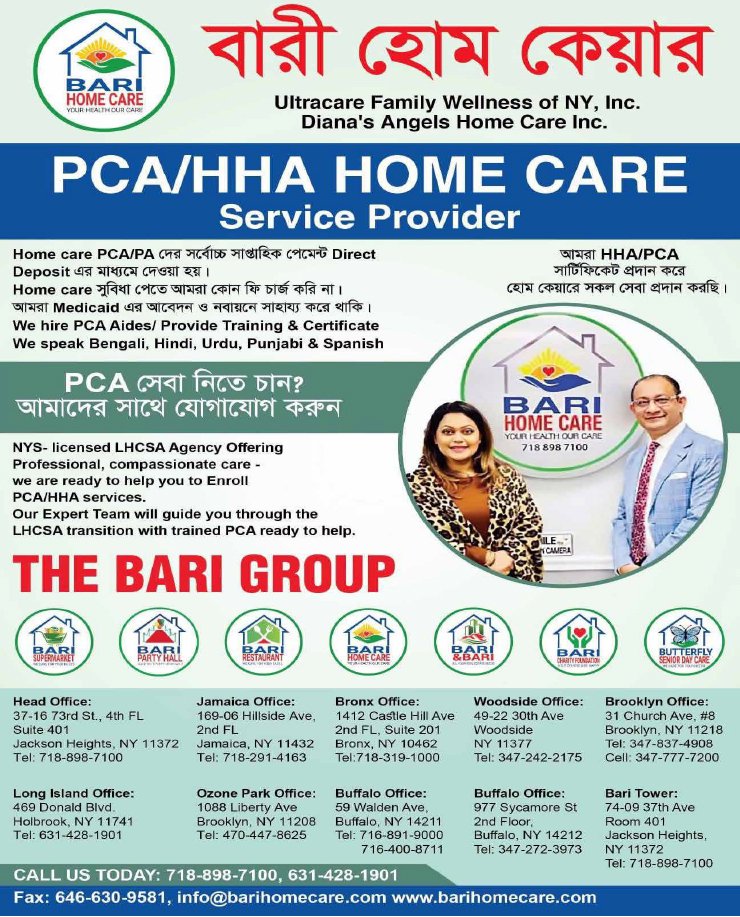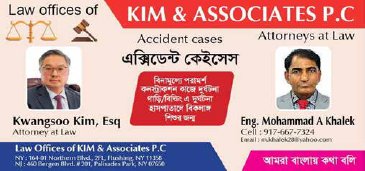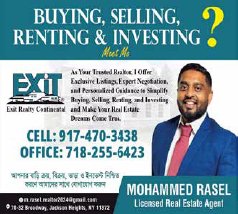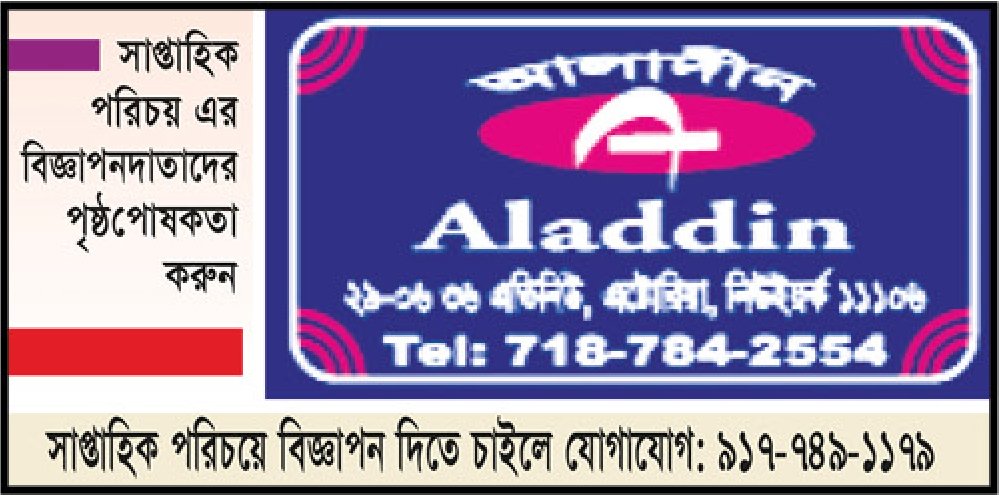

বাংলাদেশের ৪৮ শতাংশেরও বেশি মানুষ কাকে ভোট দেবেন ঠিক করতে পারছেন না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভোট নিয়ে নানা ধরনের অনিশ্চয়তার কারণে এমন সিদ্ধান্তহীনতা বাড়ছে। অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা
ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-র ‘ পালস সার্ভে ৩’-এর ফলাফলে ওই সিদ্ধান্তহীনতার চিত্র উঠে এসেছে। বলা হয়েছে ৪৮.৫ শতাংশ মানুষ কাকে ভোট দেবেন তা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি। এই প্রতিষ্ঠানটির গত বছরের অক্টোবরের একই ধরনের জরিপে এমন সিদ্ধান্তহীন মানুষের সংখ্যা ছিলো ৩৮ শতাংশ। ফলে, এই জরিপের ফল অনুযায়ী, আট মাসে কাকে ভোট দেবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীন মানুষের সংখ্যা ১০.৫ শতাংশ বেড়েছে। সর্বশেষ জরিপটি গত ১ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। সোমবার জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়। তবে একটি অংশ কে কোন দলকে ভোট দেবেন তা জানিয়েছেন। ১৪.৪ শতাংশ মানুষ কাকে ভোট দেবেন তা বলতে চান না। আর ভোট দেবেন না বলেছেন ১.৭ শতাংশ।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন- এমন প্রশ্নে ১২ শতাংশ বিএনপি, ১০.৪ শতাংশ জামায়াতে ইসলামী এবং ২.৮ শতাংশ মানুষ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কথা বলেছেন। আট মাস আগে গত অক্টোবরে একই প্রশ্ন করা হলে ১৬.৩ শতাংশ মানুষ বিএনপি, ১১.৩০ শতাংশ জামায়াত, ৮.৯ শতাংশ এ মুহূর্তে যাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ, সেই আওয়ামী লীগকে আর ২ শতাংশ মানুষ এনসিপিকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ আট মাস পর বিএনপি ও জামায়াতের ভোট কিছুটা কমেছে আর এনসিপির ভোট কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থনও ৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ৭.৩ শতাংশ হয়েছে। এর বাইরে জাতীয় পার্টির ভোট ০.৭ শতাংশ থেকে ০.৩ শতাংশ, অন্যান্য ইসলামি দলের ভোট ২.৬ শতাংশ থেকে নেমেছে ০.৭ শতাংশে।
‘‘আপনার নির্বাচনি এলাকায় কোন দলের প্রার্থী জিতবে বলে মনে হয়”-এমন প্রশ্নে ৩৮ শতাংশ মানুষ বিএনপির কথা বলেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ১৩ শতাংশ মানুষ জামায়াত ও ১ শতাংশ এনসিপির কথা বলেছেন। আর আওয়ামী লীগের কথা বলেছেন ৭ শতাংশ মানুষ। বিআইজিডি-এর ফেলো অব প্র্যাক্টিস সৈয়দা সেলিনা আজিজ বলেন, “মোট ১০ হাজার মানুষের মধ্যে টেলিফোনে এই জরিপ করা হয়। তাদের মধ্যে নারী, পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ এবং ৫২ শতাংশ। জরিপে অংশ নেয়াদের মধ্যে ৫১ ভাগ ছিলেন ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে, বাকিদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি।
সর্বশেষ জরিপে যে ১০ হাজার অংশ নিয়েছেন, তারা আগের জরিপে ছিলেন না। তবে কিছু প্রশ্ন একই ছিল। খোলাখুলি প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের, যেমন, ‘‘আপনি কোন দলকে ভোট দেবেন?” এই প্রশ্নের জবাবে কোনো দলের নাম উল্লেখ করার অপশন রাখা হয়নি। এই প্রশ্নের জবাবে তারা কোন দলকে ভোট দেবেন, ভোট দেবেন না, সিদ্ধান্ত নেননি-এই জবাবগুলো তাদের ইচ্ছায় দিয়েছেন। জরিপে ভোটের বাইরেও অন্তর্বর্তী সরকারের নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল। দুই সময়ের জরিপেই মোটামুটি ২২টি করে প্রশ্ন করা হয়। এরমধ্যে কমবেশি পাঁচটি প্রশ্ন একই ছিল। কাকে ভোট দেবেন – এই প্রশ্ন দুই সময়ের জরিপেই ছিল।
কাকে ভোট দেবেন- সেই ব্যাপারে মানুষের সিদ্ধান্তহীনতা বাড়ার কারণ জানা গেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এই জরিপে কারণ জানার চেষ্টা আমরা করিনি। আর টেলিফোনে এই ধরনের প্রশ্নের জবাবও মানুষ দিতে চায় না। তবে আমরা ইনপার্সন জরিপের পরিকল্পনা করছি। তখন হয়তো কারণ জানতে চাইবো।” বাংলাদেশের জরিপকারী সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইনফর্মেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)-র প্রতিষ্ঠাতা সিইও সাঈদ আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, “ফোন সার্ভের মধ্যে এক ধরনের বায়াসডনেস থাকে। কারুর ফোন আছে, কারুর নাই। আবার কে কোন ধরনের ফোন ব্যবহার করে তা-ও একটা বিষয়। আর এই মাধ্যমে নারীর অ্যাকসেস কম। এবং পুরুষ তাকে প্রভাবিত করে।”
তবে তার কথা,” এই ধরনের জরিপ পুরোপুরি রিপ্রেজেন্টেটিভ না হলেও বাস্তব অবস্থাকে কম-বেশি প্রতিফলিত করে। আর এখানে স্যাম্পল সাইজ ১০ হাজার। ফলে এটাকে জাতীয় জরিপ বলা যায়।” দ্বিতীয়বার আগেরবারের মানুষদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা না করার বিষয়ে তিনি বলেন,” আগের আর পরের জরিপে একই মানুষকে প্রশ্ন করার দরকার নাই এই ধরনের জরিপে। দুই জরিপেই একই প্রশ্নে আলাদা মানুষ জবাব দিলেও মানুষের মতামত উঠে আসে। কারণ, এটা র্যানডম স্যাম্পলিং। এটা এরকমই হয়।”
তার কথা, “আরো কয়েকটি সার্ভে আমরা দেখেছি। পরিস্থিতির সাথে মানুষের মত পরিবর্তন হচ্ছে। একবার উৎসাহ নিয়ে কেউ কারুর কথা বলছে, পরে দেখছে সে-ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ছে। তখন কিন্তু ওই ব্যক্তির মতের পরিবর্তন হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে ভোট হবে, আবার পরিস্থিতির কারণে তার ভোট নিয়ে সংশয় হচ্ছে। তখন তার মত বদলে যাচ্ছে। এখন যদি পরিস্থিতি দেখে মনে হয় সবাই একরকম, কোনো পরিবর্তন আসেনি, তখন হয় ভোট কাস্ট কম হবে, অথবা সিদ্ধান্তহীনতা বাড়বে। তাই হচ্ছে। এখন আবার ‘না’ ভোট ফিরে এসেছে। ফলে না ভোটের দিকেও যাবেন কেউ কেউ।”
দ্বিতীয়বার আগেরবারের মানুষদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা না করার বিষয়ে তিনি বলেন,” আগের আর পরের জরিপে একই মানুষকে প্রশ্ন করার দরকার নাই এই ধরনের জরিপে। দুই জরিপেই একই প্রশ্নে আলাদা মানুষ জবাব দিলেও মানুষের মতামত উঠে আসে। কারণ, এটা র্যানডম স্যাম্পলিং। এটা এরকমই হয়।”
তার কথা, “আরো কয়েকটি সার্ভে আমরা দেখেছি। পরিস্থিতির সাথে মানুষের মত পরিবর্তন হচ্ছে। একবার উৎসাহ নিয়ে কেউ কারুর কথা বলছে, পরে দেখছে সে-ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ছে। তখন কিন্তু ওই ব্যক্তির মতের পরিবর্তন হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে ভোট হবে, আবার পরিস্থিতির কারণে তার ভোট নিয়ে সংশয় হচ্ছে। তখন তার মত বদলে যাচ্ছে। এখন যদি পরিস্থিতি দেখে মনে হয় সবাই একরকম, কোনো পরিবর্তন আসেনি, তখন হয় ভোট কাস্ট কম হবে, অথবা সিদ্ধান্তহীনতা বাড়বে। তাই হচ্ছে। এখন আবার ‘না’ ভোট ফিরে এসেছে। ফলে না ভোটের দিকেও যাবেন কেউ কেউ।”
বিশ্লেষকরা যা বলছেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ মনে করেন, “দীর্ঘদির ধরে কর্তৃত্ববাদী শাসন ছিল। মানুষ ভোট দিতে পারেনি। এখনো দেখছে যে সরকারের পতনের পরও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাই হয়তো মনে করছে ভোট দিয়ে আর কী হবে। আগে যা ছিল তা-ই আছে। তাই তারা কাকে ভোট দেবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এবং তারা দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ। মানুষের মধ্যে হতাশার প্রতিফলন এটা।” “আবার এই টেলিফোনিক সার্ভেতে যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক, তারা হয়তো নিজেদের প্রকাশ করতে চায়নি। তাই সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানিয়েছে। আবার যে ৭ শতাংশ বলেছে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে, সে কীভাবে দেবে? অনেক প্রশ্নের উত্তর এখানো পাওয়া যাচ্ছে না,” বলেন তিনি।
তার কথা, “এখনো কয়টি দল নির্বাচনে যাবে তা নিশ্চিত নয়। কেউ কেউ আবার মনে করতে পারে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ হয়তো নির্বাচন করতে পারবে। আবার শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিস্থিতি কী হবে? সব কিছু মিলিয়ে অনেক বিষয় এখনো অমীমাংসিত। ফলে সিদ্ধান্তহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।” এই জরিপের পর অবশ্য ডিসেম্বরে তফসিল এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে নির্বাচনের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে। ফলে আগামীতে পরিস্থিতির উন্নতি হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন,” অনিশ্চয়তা এখনো আছে।”
সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল বলেন, “এখনো তো জামায়াত বলছে, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে তারা আন্দোলনে যাবে, নির্বাচনে যাবে না। এনসিপি বলছে, বিচার না হলে, সংস্কার না হলে তারা নির্বাচনে যাবে না। আবার এখন যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে, মানুষ তাতে আস্থা পাচ্ছে না। কারণ, প্রধান উপদেষ্টা বার বার নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের কথা বলছেন। ফলে মানুষ এখনো প্রশ্ন করছে – নির্বাচন কি হবে। আবার নির্বাচনে ব্যালট পেপারের চেহারা কেমন হবে তাও মানুষ বুঝতে পারছে না। নৌকা মার্কা কি থাকবে, না থাকবে না। ২০ শতাংষ মানুষ তার মার্কা খুঁজে পাবে না। তাহলে নির্বাচনটা কেমন হবে? আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কি গ্রহণযোগ্যতা পাবে? মানুষ এমন নানা বিষয় নিয়ে সন্দেহে আছে। ফলে তারা ভোটের ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।”
তার কথা,” যারা সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলছে, তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আওয়ামী লীগের ভোটার হতে পারে। টেলিফোন জরিপে কথা বলতে মানুষ ভয় পায়। কারণ, তার ফোন নাম্বার তো জরিপকারীর কাছে আছে। ফলে সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। সে পরিস্থতি দেখছে। পারিস্থিতি অনুকুল হলে সে আসলে তার মত প্রকাশ করবে।”
তার কথা,” এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, মাত্র ১২ শতাংশ মানুষ বিএনপিকে ভোট দেবে? আমরা তো মানুষের সাথে কথা বলি। আর এনসিপি জামায়াতের যে পরিমাণ ভোটের কথা বলা হয়েছে, তা-ও আমার কাছে সঠিক মনে হয় না। আসলে পরিস্থিতি বুঝে মানুষ কথা বলছে। তারা হাওয়া কোন দিকে যায় তা বোঝার চেষ্টা করছে।” – সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে