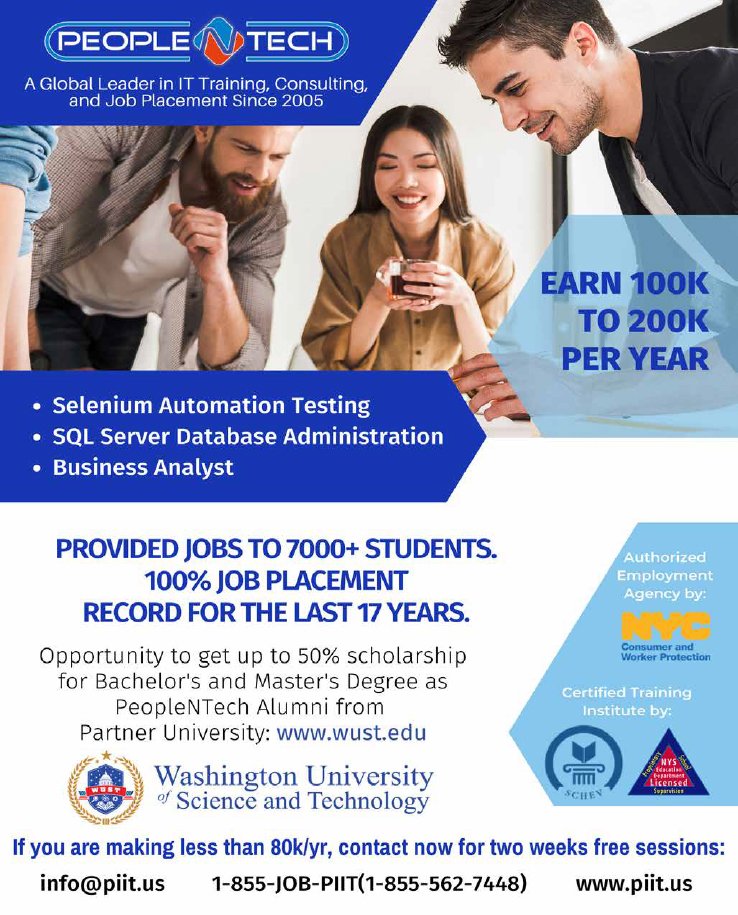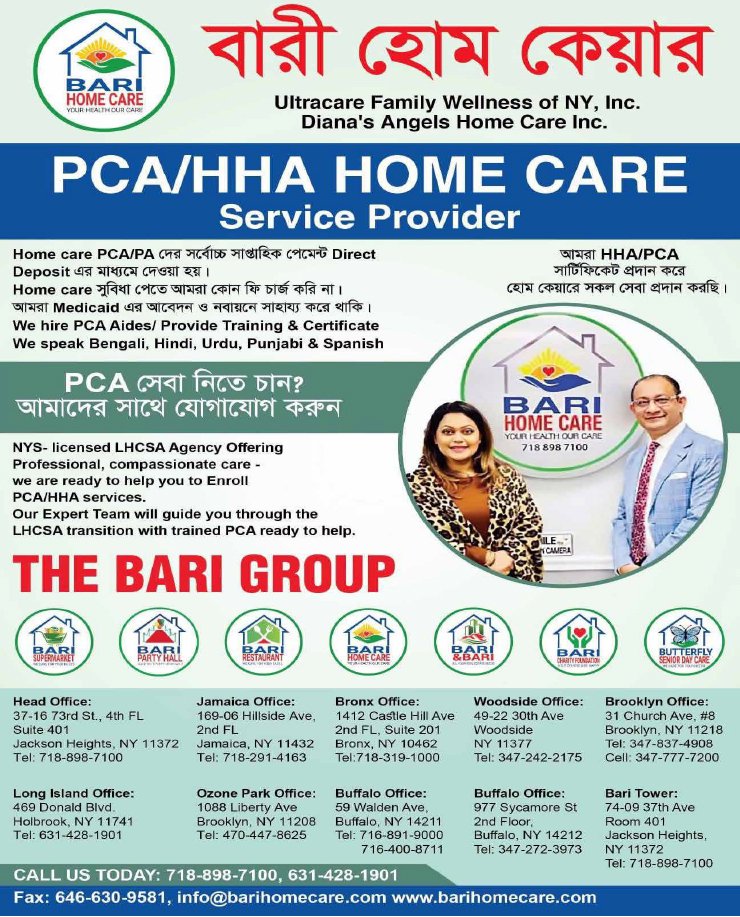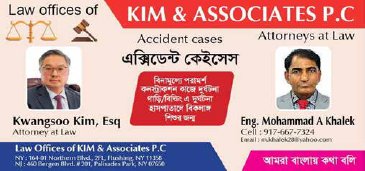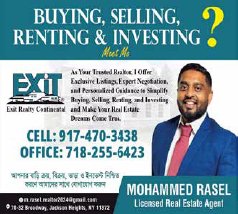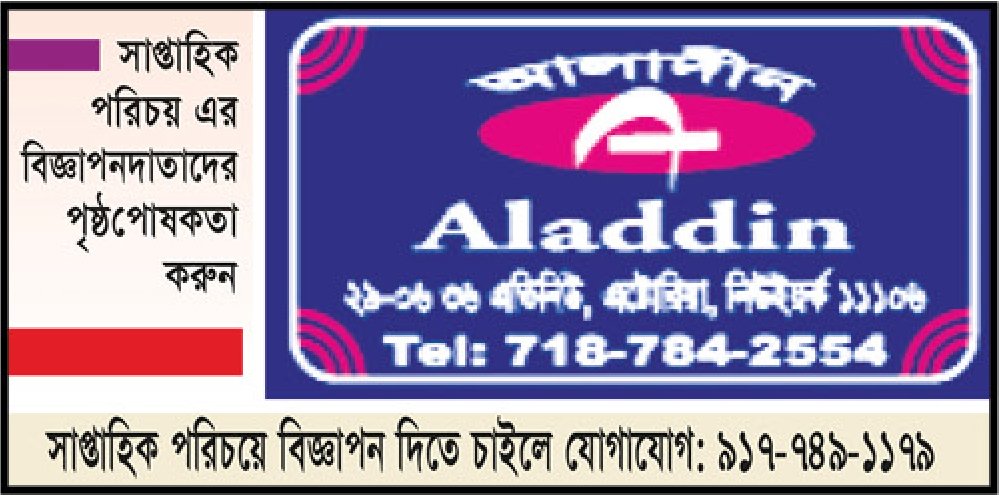

বিশ্ব অর্থনীতিতে যেন হঠাৎই ঝড় উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক পাল্টা শুল্ক আরোপ করে কাঁপিয়ে দিয়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামো। শুধু উন্নয়নশীল দেশ নয়—উন্নত অর্থনীতিগুলোও পড়েছে চাপে, জব্দ হয়েছে বহুসময়ের স্থিতিশীল হিসাব-নিকাশ।
এমন প্রেক্ষাপটে বোয়িং কেনা, খাদ্যশস্য আমদানি, এমনকি উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ—সবই একটি নরম কূটনৈতিক চাপ লাঘবের কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত যদি হয় একতরফাভাবে ঘাটতি কমানো, তাহলে বাংলাদেশের এসব ‘গুড গেসচার’ কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।
আমাদের বোঝা উচিত, যুক্তরাষ্ট্র কেবল একটি শক্তিধর রাষ্ট্র নয়, এটি একটি সুগঠিত নীতিনির্ধারক ব্যবস্থাও। তাদের বাণিজ্যনীতি একদিনে বদলায় না, আর তা বদলালেও তা হয় দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও ভূরাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে। ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর) অফিস কিংবা অন্যান্য সরকারি সংস্থা কোনো নির্দিষ্ট দেশের ‘সহানুভূতিশীল বন্ধু’ নয়—তারা কেবল আমেরিকার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় অটল। ফলে, বোয়িং কেনার মতো বড় ক্রয়াদেশ কিংবা খাদ্যশস্য আমদানির মতো সিদ্ধান্ত হয়তো আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা ইতিবাচক করতে পারে, কিন্তু সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র শুল্কে ছাড় দেবে—এমন প্রত্যাশা করা বাস্তবতা বিবর্জিত হতে পারে।
এখানে আরও একটি বাস্তবতা মাথায় রাখা জরুরি: যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক অনেক ক্ষেত্রেই আসলে ‘ঝিকে মেরে বউকে বোঝানোর’ কৌশল। অর্থাৎ, তাদের মূল টার্গেট অনেক সময় চীন, কিন্তু ‘মুক্ত বাণিজ্যের নামে সুবিধা পাওয়া’ অন্যান্য দেশকে শাস্তি দিয়ে চীনকে বার্তা দেওয়াই হয় আসল লক্ষ্য। বাংলাদেশের মতো তুলনামূলক দুর্বল অর্থনীতি তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে সেই বার্তার বাহক হয়ে পড়ে। এই মনোভাবের ফলে আমেরিকা এমন দেশগুলোকে শুল্ক দিয়ে চাপে ফেলে, যেগুলোর আসলে বড় কোনো ভূরাজনৈতিক ভূমিকা নেই। অথচ এতে ক্ষতিটা হয় ঠিক সেই দেশগুলোর, যারা রপ্তানির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি দিক অনুধাবন করা জরুরি—চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি। যুক্তরাষ্ট্র এখন তার বিশ্বজুড়ে থাকা অর্থনৈতিক অংশীদারদের ওপর বাড়তি চাপ দিয়ে তাদের চীনমুখিতা কমাতে চায়। বাংলাদেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের অবকাঠামোগত ও কৌশলগত সম্পর্ক বেড়েছে, বিশেষ করে বন্দর, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে। এমতাবস্থায় বোয়িংয়ের ক্রয়াদেশ, খাদ্যপণ্য আমদানি, এমনকি সয়াবিন ও তুলা কেনার উদ্যোগও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একধরনের ‘নৈতিক আনুগত্যের ইঙ্গিত’ হতে পারে। অর্থাৎ, এটি শুধু একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়, বরং চীন থেকে কিছুটা কৌশলগত দূরত্ব তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতায় প্রবেশের একটি রাজনৈতিক অঙ্গভঙ্গিও।
আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমনই—এখানে প্রতীকী কার্যক্রমেরও অর্থ হয়, প্রভাব পড়ে। বোয়িং কেনা কিংবা গমের মতো মৌলিক খাদ্য আমদানি আসলে এক ধরনের বার্তা: ‘আমরা কেবল রপ্তানিকারক নই, আমদানিতেও মার্কিন বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছি।’ যদিও এসব পদক্ষেপে অর্থনৈতিকভাবে বড় কোনও লাভ হবে এমন নিশ্চয়তা নেই, তবে রাজনৈতিক পয়েন্ট অর্জনের চেষ্টা হিসেবে এগুলোকে একেবারে খাটো করে দেখা যাবে না।
তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। বোয়িং কেনা বা খাদ্যশস্য আমদানি সহায়ক হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের মন জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। এজন্য চাই গভীর কূটনৈতিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাবাহিক চর্চা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোঝাপড়া। একইসঙ্গে, দেশের রপ্তানি নির্ভরতা কমিয়ে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য (ডাইভারসিফিকেশন), নিজস্ব উৎপাদন খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানো, এবং নন-ট্যারিফ ফ্যাসিলিটি অর্জনে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো এখন সময়ের দাবি।