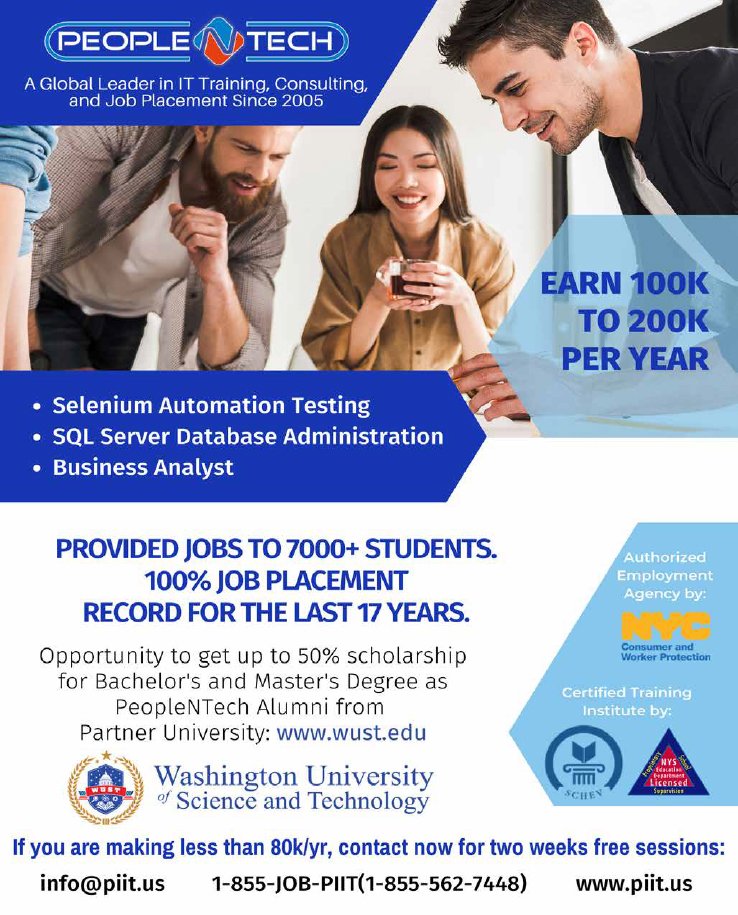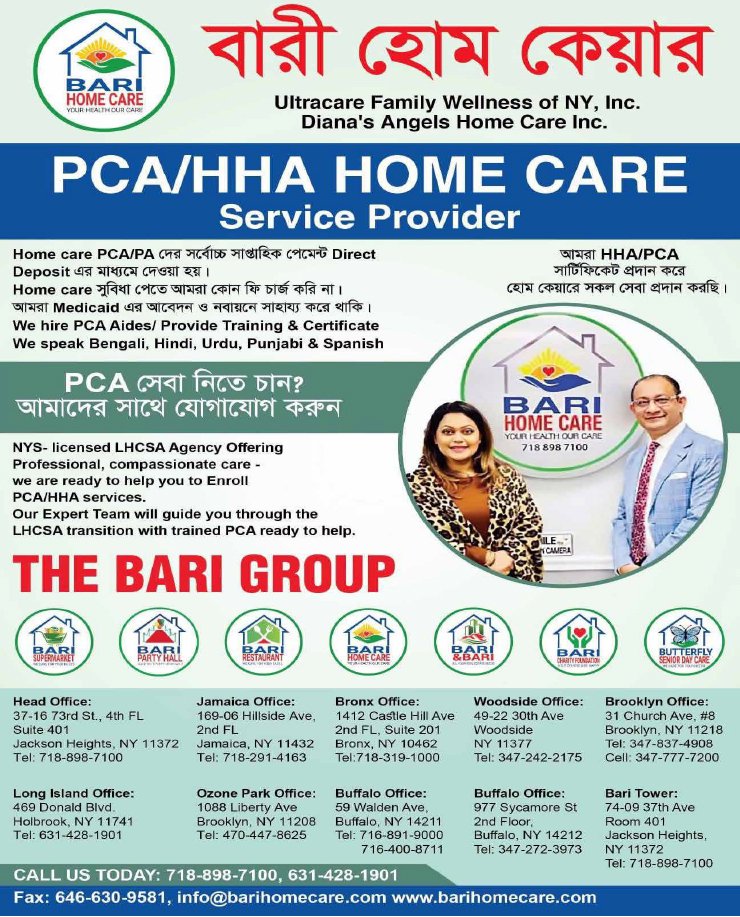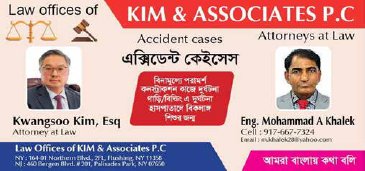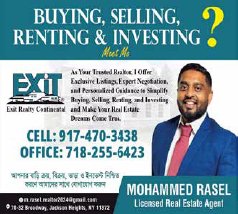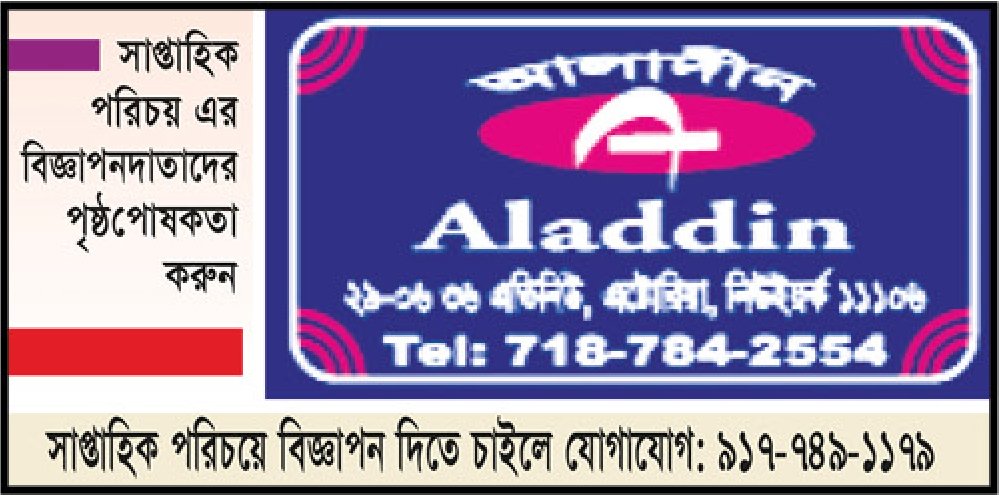

জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে যে শেখ হাসিনার পতন এবং পলায়নের এক বছরের বেশি সময় পর আমাদের কারও কারও কী হঠাৎ মনে হলো, অবৈধভাবে হাসিনার ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে দলটি কোলাবরেটর হিসেবে কাজ করেছে? আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে যাঁরা মাঠে নেমেছিলেন, তাঁরা তো একই সঙ্গে জাতীয় পার্টিসহ অন্য কোলাবরেটরদেরও নিষিদ্ধ করার কাজটা সেরে ফেলতেন ‘একই প্যাকেজে’? তা না করে এত দিন পর হঠাৎ করে কেন জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি এত কঠোর হয়ে উঠল?
জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হবে কি না, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না; কিন্তু বর্তমান সময়ের রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ‘খেলার’ এক ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে এই ইস্যু। তাই ঘুঁটি নয়; বরং ‘খেলাটা’ নিয়ে আলোচনা করা এবং বোঝা জরুরি। দীর্ঘ সময় ভয়ংকর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে এই দেশকে আক্ষরিক অর্থেই ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের ওপর যৌক্তিক ক্ষোভ জনগণের ছিল। ক্ষোভ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোরও। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পেছনে এই ক্ষোভ কাজ করেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু বিষয়টি এতটা সরল নয়। আমি বিশ্বাস করি, এর পেছনে কাজ করেছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক হিসাবও। ঠিক একই হিসাব কাজ করছে জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার দাবির পেছনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, আওয়ামী অপশাসন বাংলাদেশে জেঁকে বসা এবং টিকে থাকার পেছনে জাতীয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো ছাড়া এই রোডম্যাপ আর কেউ স্বাগত জানায়নি। জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এটাকে বলেছেন ‘সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা’। বলাবাহুল্য, দেশের রাজনীতির গভীর পর্যবেক্ষকদের কাছে জামায়াতের এই অবস্থান মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। নির্বাচন প্রশ্নে জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন তাদের ইতিবাচক অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করলেও নির্বাচন নিয়ে নানা রকম শর্ত দেওয়ায় সংশয় তৈরি করে। নির্বাচনের সঙ্গে সংস্কার, বিচার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন, এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আগামী সংসদ নির্বাচনও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে করার মতো ‘অদ্ভুত’ দাবিও শর্ত হিসেবে এসেছে। দাবি পূরণ না হলে নির্বাচন বর্জন, এমনকি প্রতিহত করার হুমকিও এসেছে।
যে সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে, সেই সরকার যদি কোনো নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার এজেন্ডা থেকে থাকে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কোনোটির নির্বাচনে না যাওয়ার যৌক্তিকতা থাকে। তাই নির্বাচনে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সব শর্ত এই বার্তা দেয়, শর্তদানকারীরা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে স্বচ্ছন্দ নয়। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হলেও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে আগামী সংসদ নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে না, এটা অনেকটাই নিশ্চিত। ফলে আমাদের নির্বাচনের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এটা প্রাথমিকভাবে অনেকেই মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় প্রধান দলে পরিণত হয়েছে, যদিও সর্বোচ্চ সমর্থনপুষ্ট দল বিএনপির চেয়ে তার অবস্থান অনেক পেছনে।
জামায়াত যদি এই ‘অনেক পেছনে’ থাকার বাস্তবতা মেনে নিতে পারত, তাহলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু দলটি ৫ আগস্ট–পরবর্তী সময়ে কিছু সময়ের জন্য হলেও হয়তো ভেবেছিল, তাদের অনেক জনসমর্থন তৈরি হয়েছে এবং নির্বাচনে তারা অনেক বেশি আসনে জয়লাভ করবে। সম্ভবত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামায়াত এবং শিবিরের অ্যাকটিভিস্টদের প্রচুর শোরগোলের কারণে দলটির মধ্যে তো বটেই, নাগরিকদের কারও কারও মধ্যে জামায়াতের জনসমর্থনের বিষয়ে বিভ্রম তৈরি হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হলে এনসিপির বয়স এক বছরও পূর্ণ হবে না। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে থাকা অনেকগুলো মুখ দলটিতে থাকার কারণে এবং অন্তর্বর্তী সরকার (প্রধান উপদেষ্টাসহ) দলটিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি সংবাদমাধ্যমে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। এর বাইরেও তারা শুরু থেকেই দামি বাণিজ্যিক ভবনে অফিস, জমকালো আত্মপ্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিসরে একটি বড় দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি কি তাদের প্রত্যাশিতসংখ্যক আসনে জিততে পারবে? যদি সেটা না পারে, যদি সংখ্যাটা তৈরিকৃত ‘হাইপ’–এর কাছাকাছিও না হয়, তাহলে দল দুটির ভবিষ্যৎ রাজনীতি বড় প্রশ্নের মুখে পড়বে। এই বিবেচনা থেকেই সম্ভবত জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার চাপ জোরদার হয়ে সামনে এসেছে। রাজনীতির পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট যে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিকে যদি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসনে জিততে হয়, তাহলে তাদের কোনো না কোনোভাবে বিএনপির সঙ্গে বড় ধরনের আসন সমঝোতায় যেতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হয়ে নির্বাচনে বিশাল জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিএনপি কেন বড় ধরনের আসন সমঝোতায় যাবে?
আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে জামায়াত ও এনসিপির বাইরে জাতীয় পার্টির আছে জনশক্তি। সমর্থনের দিক থেকেও তারা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা তো আছেনই, আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আওয়ামী সমর্থক অনেকেই জাতীয় পার্টির মার্কায় নির্বাচন করতে পারবেন, এমন জল্পনা আছে। নিজের ভোটব্যাংকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভোট যুক্ত হলে নির্বাচনের জাতীয় পার্টির প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষেত্রে জামায়াতের, এমনকি দ্বিতীয় প্রধান দল হওয়ার সম্ভাবনাও বড় হুমকির মুখে থাকবে। তার চেয়ে জরুরি কথা, জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনের মতো দল নির্বাচনে না গেলেও বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দল মাঠে থেকে যায়।
বিএনপির সঙ্গে যদি জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন স্বাভাবিক আলোচনায় আপসরফা করতে না পারে (সেটা হচ্ছে না বলে খবর বেরিয়েছে পত্রিকায়), তাহলে দলগুলো বিএনপিকে চাপ দেওয়ার পথে হাঁটবে। জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হলে এবং এই দলগুলো যদি নির্বাচনে না যায়, তাহলে নির্বাচনের মাঠে বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো ছাড়া আর কেউ থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন আদৌ হবে কি না, হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না, সেই প্রশ্ন জোরেশোরে উঠবেই। কোনো বড় রাজনৈতিক দলকে চাপে রেখে ছোট দলগুলোর কিছু রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের চেষ্টাকে সমস্যা হিসেবে না দেখাই উচিত। আমাদের এই অঞ্চলের রাজনীতিতে এই চর্চা বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু আশঙ্কা থেকে যায়, এই যাবতীয় কাজ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টায় হচ্ছে কি না। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বানচাল হয়ে গেলে দেশের যা–ই হোক না কেন, কিছু দল এবং ব্যক্তির বিরাট সুবিধা আছে তো বটেই।
বাংলাদেশ ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তুলনীয় অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে (যেমন ‘আরব বসন্ত’–এর দেশগুলো) বাংলাদেশ মোটামুটি স্থিতিশীলতার মধ্যেই ছিল এত দিন। সরকারের নানা ব্যর্থতার সমালোচনা থাকলেও সরকার একটি ভালো নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছিল এত দিন। কিন্তু এখন অস্থিতিশীলতা তৈরির একধরনের পরিকল্পনা ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। নির্বাচন বানচাল করে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি শক্তি ক্রিয়াশীল আছে।
বাংলাদেশের নির্বাচনটি ঠিক সময়ে হবে কি না, সেটার ওপর শুধু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তনই নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও। যারা নানা শর্ত দিয়ে নির্বাচন বানচাল করার কিংবা নিদেনপক্ষে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারা এই রাষ্ট্র এবং জাতির প্রতি মারাত্মক নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করছে। ১৫ বছরের ভয়ংকর অপশাসনের পর এই দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে নিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবাধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দীর্ঘ যাত্রার সূচনা করতে হবে। এর জন্য ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হতে হবে, সম্ভব হলে আরও আগে। জাহেদ উর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক