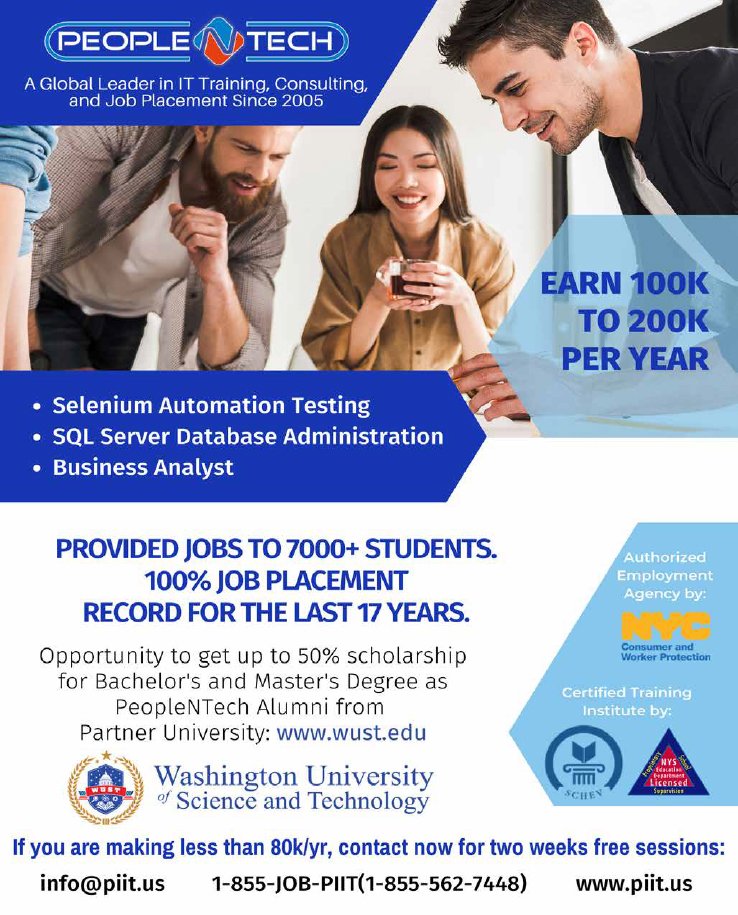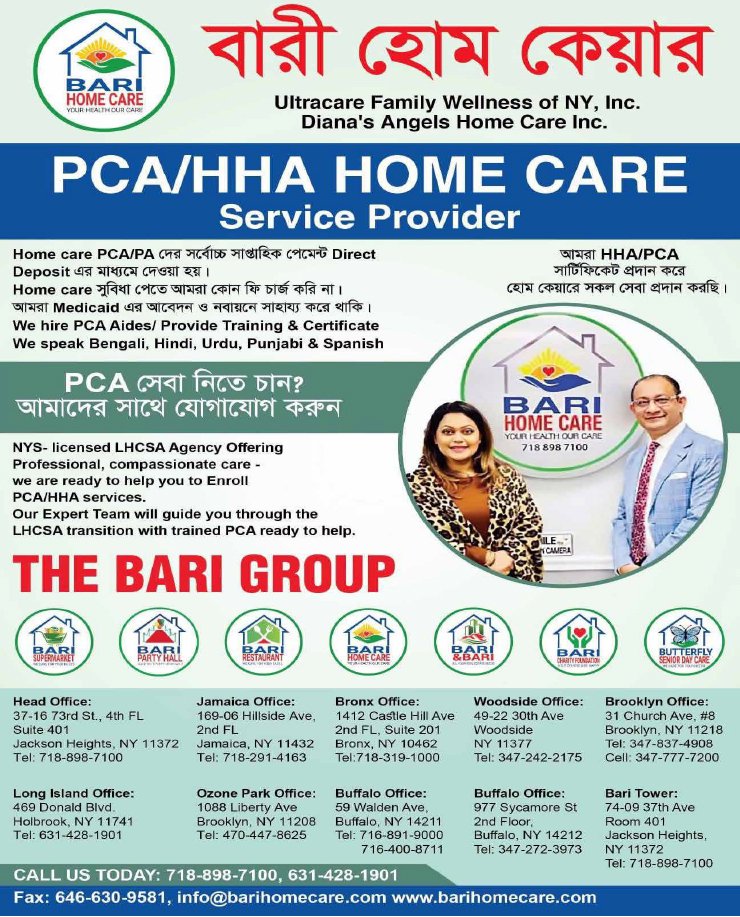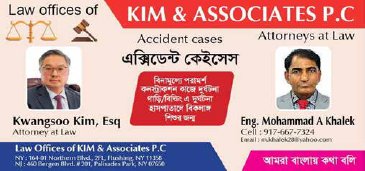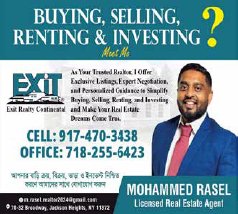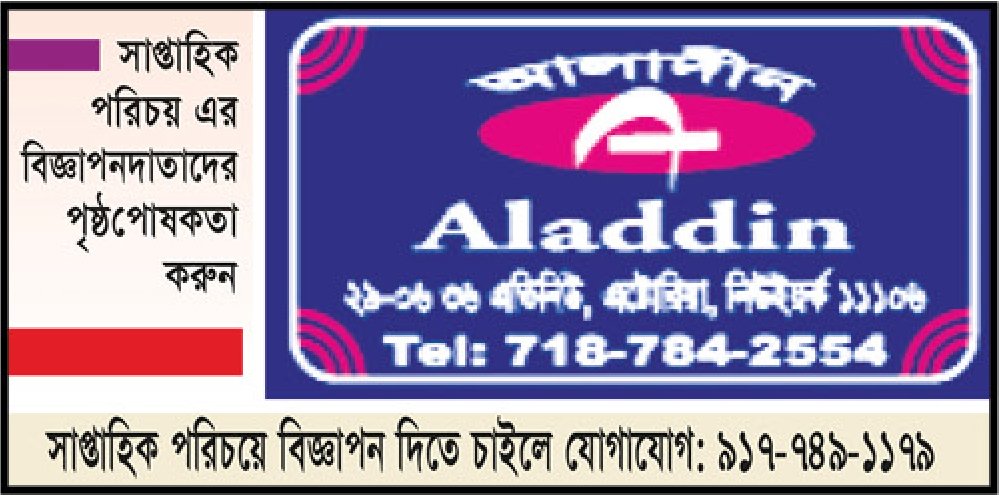
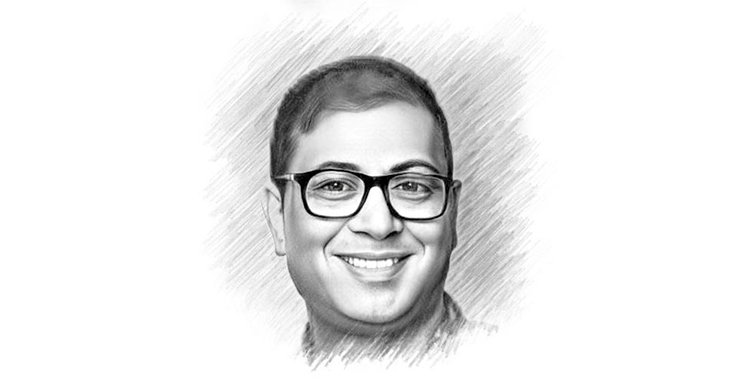
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম জে. বাউমল ২০০৭ সালে গুড ক্যাপিটালিজম, ব্যাড ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড দ্য ইকোনমিকস অব গ্রোথ অ্যান্ড প্রসপারিটি নামের গবেষণামূলক বইয়ে চার ধরনের পুঁজিবাদের কথা বলেছিলেন, যেমন রাষ্ট্রনির্দেশিত পুঁজিবাদ, বড় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুঁজিবাদ, অলিগার্কিক পুঁজিবাদ ও উদ্যোক্তাভিত্তিক পুঁজিবাদ।
নির্দিষ্ট কিছু শিল্প বা প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করে তাদের প্রবৃদ্ধি ও আধিপত্যের জন্য রাষ্ট্র সহায়তা করলে তাকে রাষ্ট্রনির্দেশিত পুঁজিবাদ বলা হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয় বড় বড় করপোরেশনের মধ্য দিয়ে। তবে এর ফলে অলিগোপলি তৈরি হয়, অর্থাৎ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্যোক্তাভিত্তিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় অসংখ্য ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা থেকে মৌলিক উদ্ভাবন আসে, যদিও বাস্তবে এমনটা খুব একটা দেখা যায় না।
অলিগার্কিক পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমিত কিছু ধনী পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। এ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষমতা ধরে রাখা ও ধনসম্পদ আরও বাড়ানো। এতে সম্পদ ও আয়ে চরম বৈষম্য তৈরি হয়, ব্যবসায় অন্যরা ঢুকতে পারে না, দুর্নীতি বাড়ে। এর প্রভাবে বিনিয়োগ কমে যায়, অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে পড়ে ও চোরদের শাসন বা ক্লেপটোক্রেসি বা ক্রনি ক্যাপিটালিজমের দেখা মেলে, যা দুঃশাসনে রূপ নেয়।
বাংলাদেশে যখন চোরতন্ত্রের দেখা মিলল: ক্লেপটোক্রেসি বা চোরতন্ত্র কথাটি প্রথম বলেছিলেন পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানিস্লাভ আন্দ্রে। তিনি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত মিলিটারি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড সোসাইটি নামের বইতে বলেছিলেন, ক্রনি শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অভিজাত শ্রেণি নিজেদের এতটাই ধনী করে তোলে যে তারা পুরো দেশকেই দরিদ্র করে ফেলে। আর তখন সেটাকে বলা হয় ক্লেপটোক্রেসি। প্রভাবশালী ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্ট নিয়মিতভাবে ক্রনি ক্যাপিটালিজম সূচক প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের সূচকে বলা হয়েছিল, ক্রনি পুঁজিপতিদের প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পদ এসেছে স্বৈরাচারী দেশগুলো থেকে। বাংলাদেশে ক্লেপটোক্রেসি বা ক্রনি ক্যাপিটালিজম, অর্থাৎ চোরতন্ত্র সবাই বেশি দেখছে প্রায় দুই দশক ধরে। এ কারণে স্ট্যানিস্লাভ আন্দ্রে ও বাউমলের কথামতোই দুর্নীতি ব্যাপক হয়েছে, অর্থনীতিও স্থবির হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ আয়বৈষম্যের দেশের একটি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আপাতত চোরতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে। তবে একেবারেই বিদায় নিয়েছে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চোরতন্ত্র দমন আসলেই কতটা সম্ভব।
চোরতন্ত্র দমন কতটা সম্ভব: আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ মোটেই সহজ নয়। এটা করতে গেলে অর্থনীতিকে একধরনের মূল্য দিতে হয়। বলা হয়, এতে অর্থনীতির ক্ষতি হয়, গতি কমে যায়। কলম্বিয়ায় মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর সেখানে অর্থনীতি আরও খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। সুতরাং অর্থনীতিকে গতিশীল ও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কালো অর্থের প্রবাহ অনেকটাই মেনে নিতে হবে। এই যুক্তিতে সরকারও কালোটাকা দমনে আগ্রহী হয় না। তবে নতুন একটি গবেষণায় এ ধারণাকে পাল্টে দেওয়ার মতো বহু উপাদান আছে। ব্রুনো বুচেত্তি, মিকেল ফাব্রিজি, এলিসাবেত্তা ইপিনো, ইক্সার্ট মিকেল-ফ্লোরেস ও আন্তোনিও পারবোনেত্তি নামের পাঁচ অর্থনীতিবিদ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ইসিবি) গবেষক। ‘সংঘটিত অপরাধ ও ব্যাংক: ঋণ প্রদানে মাফিয়াবিরোধী পুলিশি অভিযানের প্রভাব মূল্যায়ন’ নামে তাঁদের একটি গবেষণা গত জুলাই মাসে ইসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। এখানে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, অপরাধীদের ব্যবসা ভেঙে দিলে তা শুধু আইনশৃঙ্খলার জন্যই নয়, অর্থনীতির জন্যও ভালো।
গবেষণাটি করা হয়েছে ইতালির মাফিয়াদের নিয়ে। দেশটিতে মাফিয়া বা বড় অপরাধী সংগঠন চারটি। যেমন সিসিলির কোসা নোস্ত্রা, নেপলস ও আশপাশ অঞ্চলের কামোরা, কালাব্রিয়ার এনদ্রাঙ্গেটা ও পুগলিয়া এলাকার স্যাক্রা করোনা উনিতা। যেখানে সংঘটিত অপরাধ বেশি, সেখানে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। এই মাফিয়া চক্রের কারণে ইতালির অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা কম, বৈধ ও ভালো উদ্যোক্তারা পিছিয়ে এবং অর্থনীতির গতি শ্লথ। ইতালিতে মাফিয়া দমন শুরু এক দশক আগে থেকে। এর মধ্যে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায় ৭০০ মাফিয়া-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়েছে বা বাজেয়াপ্ত করেছে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, মাফিয়ানিয়ন্ত্রিত কোম্পানি বন্ধ হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। যেমন মাফিয়া প্রতিষ্ঠান বন্ধ করায় বৈধ ব্যবসায় ঋণ বেড়েছে দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ১ শতাংশ পর্যন্ত, স্থানীয় কোম্পানিগুলো নতুন ঋণ নিয়েছে প্রায় ৩৬০ কোটি ইউরো। উৎপাদনশীলতা বেড়েছে গড়ে এক থেকে দেড় শতাংশ পর্যন্ত।
উপসংহারে গবেষকেরা বলেছেন, সংঘটিত অপরাধ দমন কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ নয়, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও একটি হাতিয়ার। অপরাধ দমন করলে ব্যবসার পরিবেশ ভালো হয়, যা বিনিয়োগকে আকর্ষণ করে। ফলে সবারই উচিত, অপরাধ দমনকে অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ করা। এ জন্য যে খরচ হয়, তাকে ব্যয় হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা উচিত।
মাফিয়া দমন: বাংলাদেশ স্টাইল: মাফিয়া মূলত ইতালির অপরাধী চক্র। তবু কথাটা বিশ্বের প্রায় সব অপরাধী চক্রের ক্ষেত্রেই প্রতীকী পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় দুই দশকে যে অলিগার্কিক পুঁজিবাদ বা চোরদের শাসন দেখা দিল, তাদেরও মাফিয়া বলা হচ্ছে। এক ব্যক্তির হাতে ১১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার উদাহরণ সম্ভবত আর কোনো দেশে নেই।
এমন নয় যে এস আলম এতগুলো ব্যাংকের মালিক হয়ে স্যামসাং, এলজি বা হুন্দাইয়ের মতো বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। বরং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে অর্থ তুলে নিয়ে পাচার করেছে। বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ ছিল বেক্সিমকো গ্রুপের সামনেও। কিন্তু তারাও বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেছে মূলত ব্যাংক ও শেয়ারবাজার থেকে অর্থ লুট করার জন্য। বাংলাদেশে মাফিয়াদের মতোই রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠা চক্র পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করেছে কেবল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই। এর বিনিময়ে পেয়েছে অর্থ আত্মসাতের অবাধ সুযোগ। সেই অর্থের বড় অংশই পাচার হয়ে গেছে অন্য দেশে।
অন্তর্বর্তী সরকার এখন চেষ্টা করছে পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে। যদিও কাজটি মোটেই সহজ হবে না। দেশেই প্রায় আড়াই হাজার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা অর্থের পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। জেলে আছেন অনেকে, দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি। আবার বেশ কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি হারিয়েছে ৬০ হাজারের বেশি শ্রমিক। সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ২০১৯ সাল থেকে। কোভিড মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের পরে বিগত সরকার অর্থনীতি ঠিক পথে রাখতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অর্থনীতি যতটা গতিশীল হবে আশা করা হয়েছিল, সেটা হয়নি।
অন্তর্বর্তী সরকার এসে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই, তবে এ জন্য অর্থনীতির গতিকেও শ্লথ করে রাখতে হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ব্যবসায়ীরা সরে গেলেও উদ্যোক্তারা এখনো আস্থাহীন। সব ধরনের বিনিয়োগেই মন্দা চলছে। বেসরকারি খাতে ঋণ ব্যাপকভাবে কমেছে, ফলে নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে না। দেশে মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আর্থিক অপরাধ দমনের পদক্ষেপ নিলে সাধারণভাবে অর্থনীতিতে যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা, তা প্রায় সবই বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি বাংলাদেশ আর্থিক অপরাধ দমন করবে না, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না?
ইতালিতে মাফিয়া দমনের কারণে আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কমেছে চাঁদাবাজি। বাংলাদেশের সংকট এখানেই। এটা ঠিক যে এখন সুদহার বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে বিনিয়োগ না হওয়ার প্রধান কারণ সুদহার নয়। অবকাঠামো ও জ্বালানিসংকট, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, আমলাতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা, চাঁদাবাজি—এ রকম অনেক কারণ রয়েছে, যার কোনোটারই সুরাহা হয়নি। নতুন করে যুক্ত হয়েছে অব্যাহত ‘মব সন্ত্রাস’। সুতরাং কেবল ব্যাংক হিসাব জব্দ করাটাই যথেষ্ট নয়। ব্যাংক হিসাব জব্দসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, সেটা পরিষ্কার হতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরণে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা–ও ঠিক করতে হবে।
ইতালি মাফিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুটি আইন করেছিল। একটি আইন ছিল মাফিয়াদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য। দ্বিতীয় আইনটি করা হয় বাজেয়াপ্ত সম্পদের সামাজিক ও উৎপাদনশীল ব্যবহার নিয়ে। এই আইনের বলেই মাফিয়াদের বাজেয়াপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে সেখানে বড় ধরনের সমবায় আন্দোলনও হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার যেসব সম্পদ জব্দ করেছে, তার পরিণতি কী হবে, তা–ও ঠিক করতে হবে।
আসলে সব পদক্ষেপ হতে হবে সমন্বিত এক পরিকল্পনার অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের উদ্যোগের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদক্ষেপের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে থাকলে, আইনি ব্যবস্থা একই তালে না চললে, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত তথ্য ও প্রমাণনির্ভর না হলে কোনো সাফল্যই আসবে না। এতে আর্থিক অপরাধ কমবে না, কেবল অপরাধীর পরিবর্তন ঘটবে। এসব হচ্ছে না বলে চোরতন্ত্র দমনে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ইতিবাচক কিছু করতে পারবে—এমনটা আশা না করাই ভালো।
‘প্রিয় চাঁদাবাজ’দের উদ্দেশে: লিবারো গ্রাসি নামের একজন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী ১৯৯১ সালের ১০ জানুয়ারি এক স্থানীয় সংবাদপত্রে ‘প্রিয় চাঁদাবাজ’ শিরোনামে একটি খোলাচিঠি লিখেছিলেন। আরও অনেক ব্যবসায়ীর মতো তাঁকেও চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। চিঠিতে লিবারো গ্রাসি লিখেছিলেন, ‘আমাদের ওই অচেনা চাঁদাবাজকে আগে থেকেই জানিয়ে দিতে চাই, হুমকি দেওয়ার জন্য ফোনকল করা বা বোমা, গুলি কেনার জন্য টাকা খরচ করার দরকার নেই। আমরা কোনো চাঁদা দেব না। ’চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল মাফিয়া গ্রুপ কোসা নোস্ত্রার কাছে তা ক্ষমাহীন অপরাধ। ১৯৯১ সালের ২৯ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটায় বাড়ির কাছেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল লিবারো গ্রাসিকে। লিবারো গ্রাসিকে মনে রেখেই ইতালিতে আদ্দিওপিজ্জো আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালে। ইতালি ভাষায় ‘পিজ্জো’ মানে হচ্ছে চাঁদা এবং ‘আদ্দিও’র অর্থ বিদায়। সাত বন্ধু মিলে চাঁদা না দেওয়ার এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ফলে অনেক এলাকাতেই এখন ব্যবসায়ীরা চাঁদা দেন না।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর এ রকম কিছুও তো হতে পারত। কিছুই হয়নি। চাঁদা বন্ধ হয়নি, কেবল চাঁদাবাজের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ শক্তি প্রদর্শনের কাঠামোর কোনো বদল হয়নি, কেবল কিছু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর দৃশ্যমান উন্নতি বেশি অর্থনীতিতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কতটা টেকসই হবে, সেই সংশয় থেকেই গেল। শওকত হোসেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন