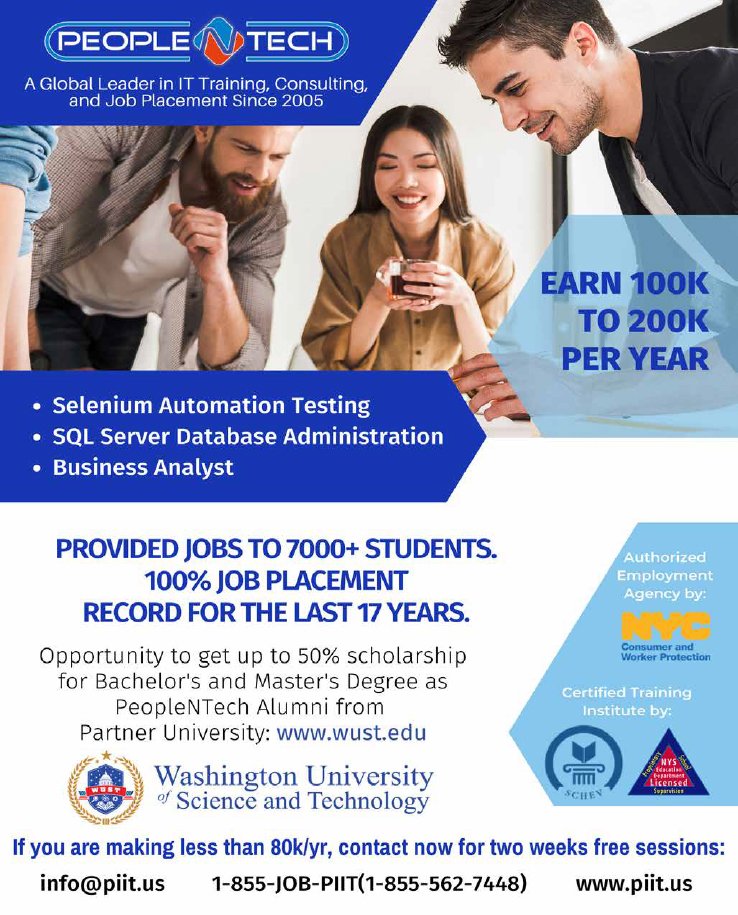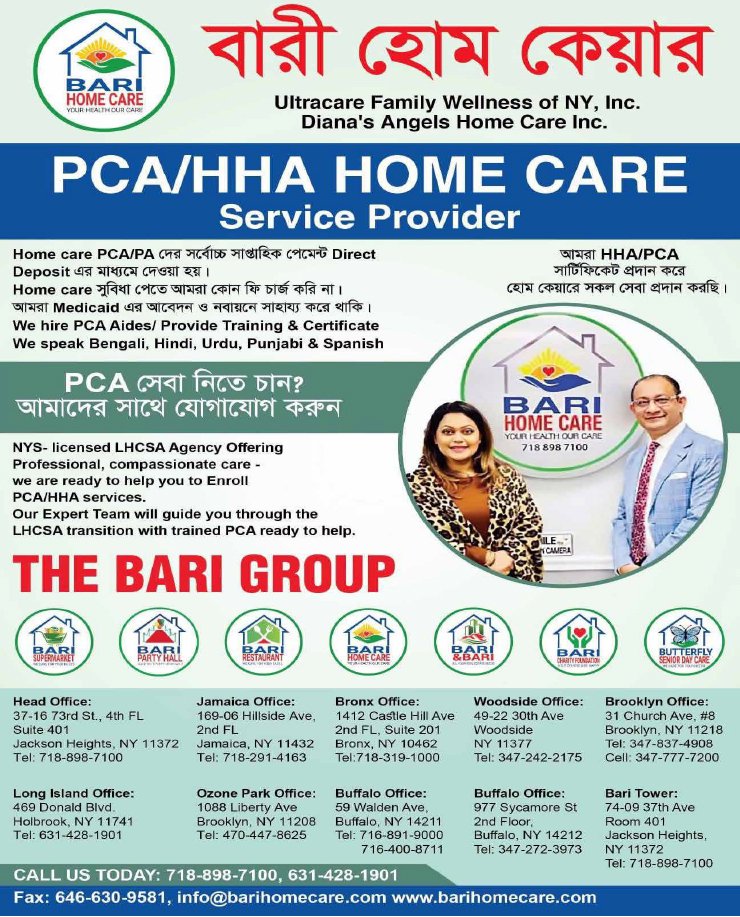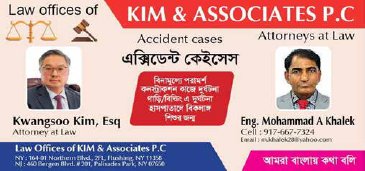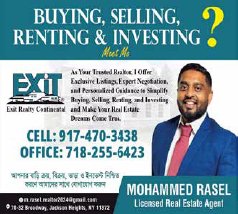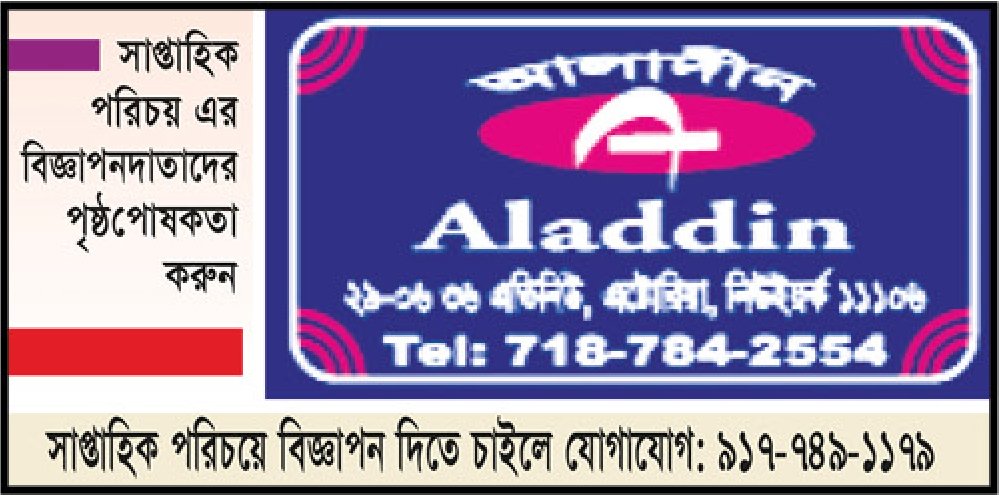

ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার যখন বলেন, একাত্তরের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ‘দুবার সমাধান’ হয়ে গেছে, তখন তা অর্ধশতাব্দীর ক্ষতকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তার চেয়েও গুরুতর শোনায় তার পরের মন্তব্যটি, যেখানে তিনি বাংলাদেশকে ‘হৃদয় পরিষ্কার’ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
আমাদের এত মানুষকে হত্যা করে হৃদয় পরিষ্কার করতে বলা ইসহাক দারের এ উক্তি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা দেখা যাচ্ছে। অনেকে এটাকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন।
যা-ই হোক, আজ আমরা ইসহাক দার যে দুটি ঘটনাকে ‘সমাধান’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোর একটু গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি:
ক. ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি এবং
খ. ২০০২ সালে পারভেজ মোশাররফের ঢাকা সফরকালে ‘অনুশোচনা’ প্রকাশ।
দেখার বিষয়, এ দুই ঘটনা কি সত্যিই একাত্তরের গণহত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের নিষ্পত্তি করতে পারে? আন্তর্জাতিক আইন কী বলে?
তবে আশার খবরটা আগে জানাই। হৃদয় পরিষ্কারের কথা বলার পর ইসহাক সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলাপ শেষে তিনি দুবার সমাধানের যে দাবি করেছেন, সে বিষয়ে একমত কি না, তা সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমি অবশ্যই একমত নই। একমত হলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমরা আমাদের অবস্থান বলেছি। তাঁরা তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনটি বিষয়ই তুলে ধরেছি।’
উপদেষ্টা আবারও তিনটি মূল অমীমাংসিত বিষয় তুলে ধরেন:
১. গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা;
২. সম্পদের ন্যায্য বণ্টন; এবং
৩. আটকে পড়াদের প্রত্যাবর্তন
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যে পরিষ্কার, দুই দেশের মধ্যে একগুচ্ছ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও মূল ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
১৯৭৪ সাল: ভুট্টো, স্বীকৃতি ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আসল প্রকৃতি
ইসহাক দারের দাবির প্রথম ভিত্তি হলো ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। এই চুক্তিকে বুঝতে হলে এর পটভূমি ছোট করে বোঝা জরুরি। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল হয় ত্রিপক্ষীয় চুক্তি।
চুক্তির মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী মানবিক সংকটগুলোর সমাধান। এই চুক্তির আওতায় পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি ও ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তন এবং ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার স্থগিত করার মতো বিষয়গুলো ছিল।
চুক্তির বয়ানে উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ‘ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট’ আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপমহাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতির স্বার্থে বাংলাদেশ ‘ক্লেমেন্সি’ বা করুণা প্রদর্শন করে বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এই চুক্তির আওতায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্থগিত হওয়া নিয়ে বিতর্ক আছে নানা মহলে; কিন্তু একে কোনোভাবেই একাত্তরের গণহত্যার ‘নিষ্পত্তি’ বা ‘সমাধান’ বলা যায় না।
এর কারণ, এই চুক্তি কোনোভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা ছিল না। চুক্তিতে পাকিস্তান তার সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার জন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় দায় স্বীকার করেনি, ক্ষমাও চায়নি; বরং এটিকে বলা যায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক উদারতা।
আবার চুক্তির আওতায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত হওয়া কোনো আইনি দায়মুক্তি ছিল না। সেই বিচার না করার সিদ্ধান্তটি ছিল একটি রাজনৈতিক সমঝোতা, যা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধের রাষ্ট্রীয় দায় থেকে পাকিস্তানকে মুক্তি দেয় না।
তাই পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ছিল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের একটি প্রক্রিয়া, ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নয়। একে ‘সমাধান’ হিসেবে উপস্থাপন করা ইতিহাসের একটি বিকৃত পাঠ।
২০০২ সাল: পারভেজ মোশাররফের সফর এবং ‘অনুশোচনা’ বনাম ‘ক্ষমা প্রার্থনা’
ইসহাক দারের যুক্তির দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো ২০০২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের ঢাকা সফর। পারভেজ মোশাররফ সেই সফরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর বিবৃতিতে ১৯৭১ সালের ‘এক্সেস’ বা ‘বাড়াবাড়ি’র জন্য রিগ্রেট তথা অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তিনি একই সঙ্গে ‘অতীতকে কবর’ দেওয়ার আহ্বান জানান; কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির নিরিখে এই মন্তব্যের সীমাবদ্ধতা মারাত্মক।
অনুশোচনা বনাম ক্ষমা—এই দুটি শব্দের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ‘রিগ্রেট’ একটি দুর্বল ও অস্পষ্ট অভিব্যক্তি, যা কোনো ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে; কিন্তু দায় স্বীকার করে না। অন্যদিকে একটি ‘ফরমাল অ্যাপোলজি’ বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনায় সুস্পষ্টভাবে দায় স্বীকার করা হয় এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়।
মোশাররফ সচেতনভাবে ‘অ্যাপোলজি’ শব্দটি এড়িয়ে ‘রিগ্রেট’ ব্যবহার করেছিলেন, যা দায়বদ্ধতা এড়ানোর একটি ‘ক্ল্যাসিক কূটনৈতিক কৌশল’। এই ভাষাগত পার্থক্যই প্রমাণ করে, ২০০২ সালের ঘটনাটি কোনোভাবেই একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষমা ছিল না, যা বাংলাদেশ দাবি করে আসছে।
পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়ার কথা সামনে এলে দাবি করা হয় যে, ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফরে এসে ‘তওবা’ শব্দটি ব্যবহার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যা তৎকালীন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও আসে। একই বছর ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আলোচনায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ‘গভীর অনুশোচনা’ প্রকাশের কথাও দলিলে উল্লেখ আছে।
পরবর্তী সময়ে ২০০২ সালে পারভেজ মোশাররফ ঢাকায় স্মৃতিসৌধের পরিদর্শক বইয়ে একাত্তরের ‘বাড়াবাড়ি’কে, ‘অনুতাপযোগ্য’ বলে উল্লেখ করেন। এমনকি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও এক টিভি টক শোতে ক্ষমা চাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।
কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ‘ক্ষমা’ হিসেবে দাবি করা এ ঘটনাগুলো ছিল হয় ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, নয়তো কূটনৈতিক ভাষা; যা ‘আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমা’র সমতুল্য নয়। কোনোটিই পাকিস্তানের পার্লামেন্টে গৃহীত হয়নি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গণহত্যার দায় স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা হিসেবে বাংলাদেশের কাছে পাঠানো হয়নি। এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ সমাধান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।
আন্তর্জাতিক আইন কী বলে : যখন একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে, (গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ), তখন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার জন্মায়। আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের ‘রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা-সংক্রান্ত খসড়া ধারা’ আর্টিকেলস অন স্টেট রেসপনসিবিলিটি ২০০১ অনুযায়ী, প্রতিকার বা ‘রিপারেশন’-এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো ‘স্যাটিসফ্যাকশন’ বা সন্তোষ, যা মূলত অবস্তুগত ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আইএলসির ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ‘স্যাটিসফ্যাকশন’-এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:
১. লঙ্ঘনের স্বীকারোক্তি (অ্যাকনলেজমেন্ট অব দ্য ব্রিচ)
২. অনুশোচনা প্রকাশ (এক্সপ্রেশন অব রিগ্রেট)
৩. আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা (ফরমাল অ্যাপোলজি)
আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে এই ধারা অনুযায়ী, ‘রিগ্রেট’ ও ‘অ্যাপোলজি’ উভয়ই ‘স্যাটিসফ্যাকশন’-এর অংশ হতে পারে; কিন্তু এর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ভাষার স্পষ্টতা, দায় স্বীকারের মাত্রা ও আন্তরিকতার ওপর। মোশাররফের ‘রিগ্রেট’ ছিল একটি অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ, বাকি রাস্তাটুকু না হাঁটা হলে দায় স্বীকারের মূল শর্ত পূরণ হয় না।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৬০/১৪৭ (২০০৫), যা ‘প্রতিকার ও প্রতিকারের অধিকারসংক্রান্ত মৌলিক নীতি ও নির্দেশিকা’ হিসেবে পরিচিত, ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী কাঠামো হাজির করে। এটি চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেয়:
১. সত্য জানার অধিকার (রাইট টু ট্রুথ)
২. ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার (রাইট টু জাস্টিস)
৩. প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (রাইট টু রিপারেশন)
৪. পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টিস অব নন-রিকারেন্স)
এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডগুলোর আলোকে বিচার করলে পাকিস্তানের ‘দুবার সমাধান’ তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। তারা সত্যকে পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি, ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিকার দেয়নি।
দ্বিতীয়ত অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা আজও ফেরত দেয়নি পাকিস্তান। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই পাওনার পরিমাণ ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পাওনার মধ্যে রয়েছে অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদে ন্যায্য ভাগ, ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের আত্মসাৎকৃত বিদেশি সাহায্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা।
ইসহাক দারের ‘হৃদয় পরিষ্কার’ করার পরামর্শ ভুক্তভোগীর যন্ত্রণাকে উপহাস করার শামিল। এটি প্রমাণ করে যে পাকিস্তান এখনো তার অতীত কৃতকর্মের গভীরতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ। ক্ষমা কোনো দয়া বা করুণার বিষয় নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রক্রিয়া, যার সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত আমাদের শেখায়, একটি অর্থবহ ক্ষমা কেমন হওয়া উচিত।
আমরা দেখি, হলোকাস্টের পর জার্মানি কেবল মৌখিক ক্ষমা চায়নি; বরং ইসরায়েল ও ইহুদি সংগঠনগুলোর সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষতিপূরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার নাম ছিল ১৯৫২ সালের লুক্সেমবার্গ চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যা ছিল দায় স্বীকারের বাস্তব প্রতিফলন।
এ শতকেই আমরা দেখেছি, উত্তর আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ সেনাদের হাতে ১৪ জন নিরস্ত্র নাগরিক হত্যার ৩৮ বছর পর দীর্ঘ বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একটি দ্ব্যর্থহীন ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যা ঘটেছিল, তা ছিল ‘আনজাস্টিফায়েড অ্যান্ড আনজাস্টিফিয়েবল’ (অসমর্থনযোগ্য ও অন্যায়)। এই ক্ষমা ছিল সুনির্দিষ্ট, দায় স্বীকারের একটি রেফারেন্স।
অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগোতে হলে পাকিস্তানের ‘দুবার সমাধান’ বা ‘হৃদয় পরিষ্কার’ করার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবস্থান থেকে সরে এসে একটি বাস্তবসম্মত ও সম্মানজনক পথে হাঁটতে হবে। এর একটি রূপরেখা হতে পারে এমন:
১. একটি যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান একাত্তরে সংঘটিত অপরাধগুলোকে ‘গণহত্যা’ ও ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ’ হিসেবে স্বীকার করে নেবে।
২. পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে, যা রাষ্ট্রীয় দলিলে নথিভুক্ত থাকবে।
৩. দুই দেশের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের নিয়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা একাত্তরের ঘটনাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরবে এবং দুই দেশের পাঠ্যপুস্তকে তা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে।
৪. অমীমাংসিত সম্পদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য একটি নিরপেক্ষ সালিসি বা টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধান প্যাকেজ তৈরি করবে।
পাকিস্তানকে বুঝতে হবে, ক্ষমা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং নৈতিক শক্তি ও ঐতিহাসিক পরিপক্বতার লক্ষণ। ‘হৃদয় পরিষ্কার’ করার দায়িত্ব বাংলাদেশের নয়; বরং পাকিস্তানের গণহত্যার দায় স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে ও অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ন্যায্য সমাধান করে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হলে অতীতের হিসাব মেটাতেই হবে। কারণ, ন্যায়বিচারকে কবর দিয়ে কোনো স্থায়ী শান্তি বা বন্ধুত্ব নির্মিত হতে পারে না।
সমাধানের পথ এখনো খোলা, তবে সেই পথে হাঁটার প্রথম পদক্ষেপটি পাকিস্তানকেই নিতে হবে। আরিফ রহমান গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মী