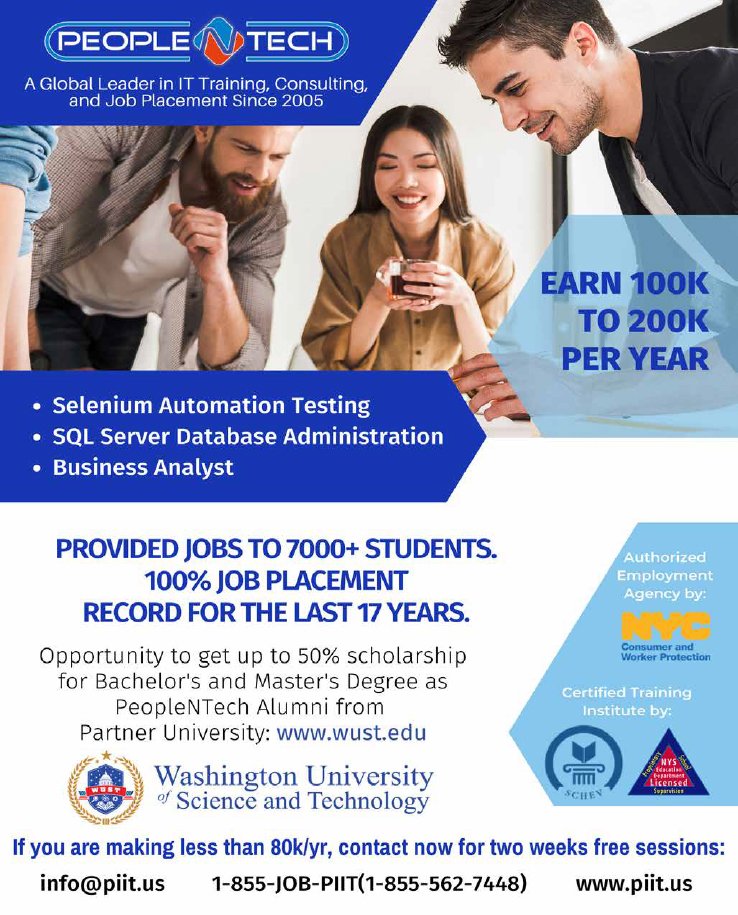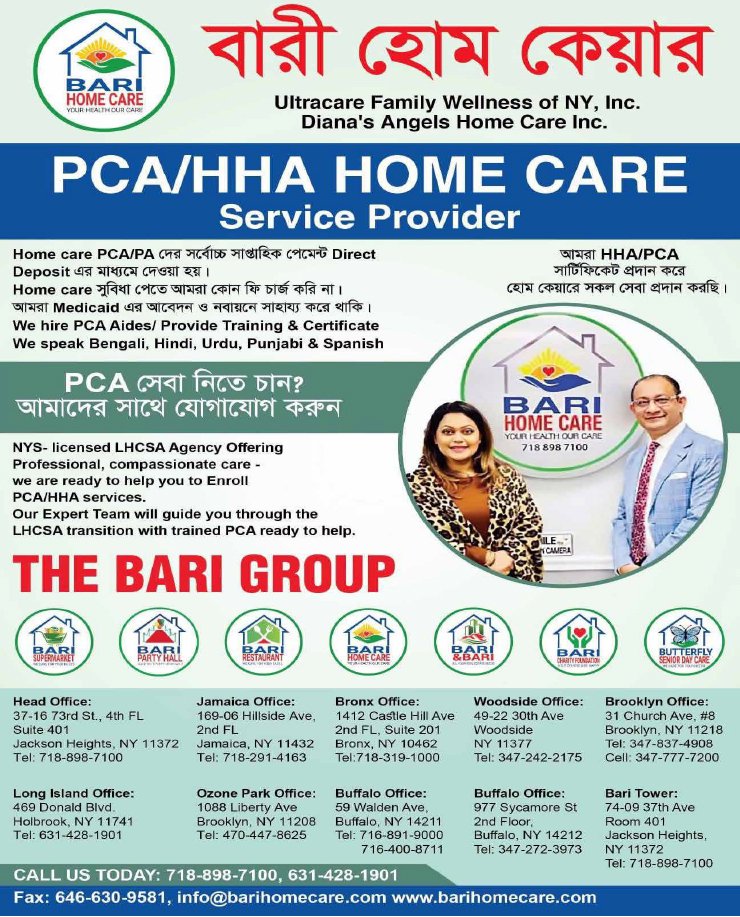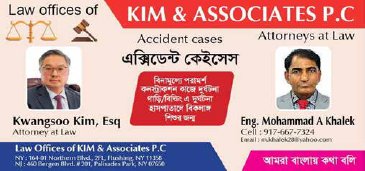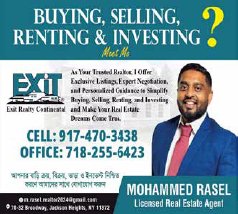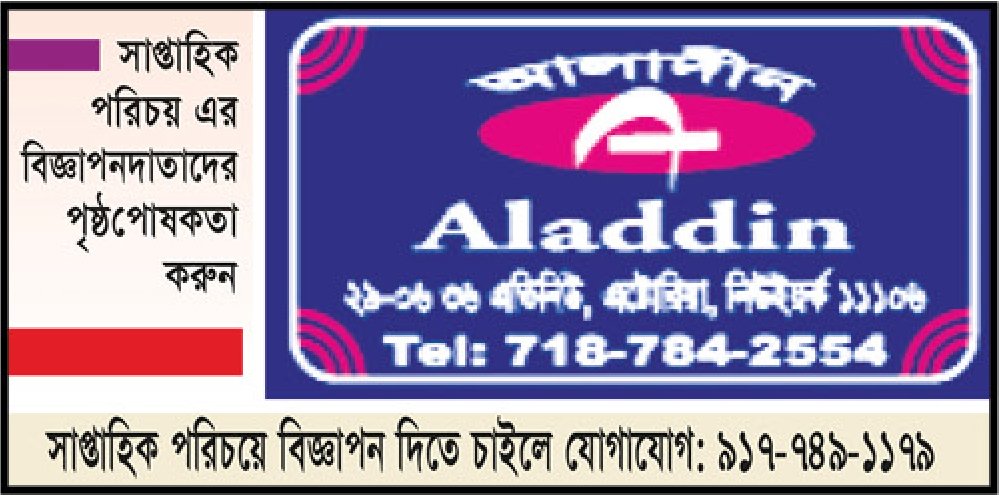

গুজবে কান দেবেন না’ বা ‘দেয়ালেরও কান আছে’ কথাগুলো আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত। কিন্তু তারপরও আমাদের জনজীবনে গুজবের বিস্তার ও এর প্রভাব এড়ানো যাচ্ছে না। গুজব বা অপপ্রচারের মতো বিষয়গুলো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত করছে প্রতিনিয়ত।
গুজবের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি, ধর্মীয় সহিংসতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে।
সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, গুজব হলো জনসাধারণ–সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি নিয়ে মুখে মুখে প্রচারিত কোনো বর্ণনা বা গল্প।
তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্রুত প্রসারণের ফলে আমাদের সমাজে অপতথ্যের একটি সংস্কৃতি জন্ম হয়েছে। এ অপতথ্য-সংস্কৃতি প্রবল শক্তিশালী; সেটি ছড়ানো অপতথ্য দিনকে রাত করে দেয়, সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেয়, নিশ্চিত বিষয়কে অনিশ্চিত করে দেয়। কেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই নয়, মূলধারার গণমাধ্যম ব্যবহার করেও অনেক সময় গুজব ছড়ানো হয়।
কয়েক দশক আগে ১৯৮৭ সালে ‘ঢোলকলমি’র গুজব যখন ছড়ায়, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল না। তখন মূলধারার গণমাধ্যম ব্যবহার করেই এই গুজবের ডালপালা ছড়িয়েছিল। প্রথম ছিল, এই গাছের পাতা গায়ে লাগলে মানুষ মারা যায়; তারপর বলা হলো, এই গাছে যে পোকা বসে তা গায়ে লাগলে বা কামড় দিলে মানুষ মারা যায়। কিন্তু পরে দেখা গেল পুরোটাই ছিল গুজব। কিন্তু গুজবের হিড়িকে সারা দেশে সাধারণ মানুষ গণহারে, এমনকি প্রশাসনও ঢোলকলমি গাছ কেটে সাবাড় করেছিল।
ইতিহাসজুড়ে গুজবকে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রচার, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলে কারসাজি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের জন্য সাম্প্রদায়িক উসকানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ‘কর্পস ফ্যাক্টরি’ গুজব ছড়িয়ে দাবি করা হয়েছিল যে জার্মানরা নিজস্ব সৈন্যদের মৃতদেহ ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করছে, এটি যুদ্ধকালীন প্রোপাগান্ডা হিসেবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। আরব বসন্তের সময় তিউনিসিয়ায় ফেসবুক ও টুইটারের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজবের দ্রুত বিস্তার ঘটতে দেখা যায়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও গুজব ছড়ানোর প্রবণতা ও এর প্রভাব ভয়াবহ। পদ্মা সেতু নির্মাণে শিশুদের মাথা লাগবে—এমন গুজবে সারা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে রাজধানীর বাড্ডায় তাসলিমা রেনু নামের এক নারীকে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা এখনো আমাদের বিস্মৃত হয়নি।
গত আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর গুজব প্রচারের ধারায় নতুন নতুন ইস্যু যুক্ত হয়, যা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে। এসব ইস্যুর মধ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ভিন্নধর্মাবলম্বীদের স্থাপনায় হামলা–ভাঙচুর, নিহত পুলিশের সংখ্যা নিয়ে গুজব, অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপতথ্য, বিভিন্ন উপদেষ্টার নামে ছড়ানো ভুয়া মন্তব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ধরনের গুজবের সূত্র হিসেবে ‘চালাইদেন’ শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল।
যেকোনো দুর্যোগ বা সংকটকালে গুজব ছড়ানোর প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ পরিস্থিতিসহ যেকোনো সংকটে গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক এবং উদ্বেগকে বাড়িয়ে জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
মূলধারার গণমাধ্যম ছাড়াও বিশ্বায়নের এই যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি, যে কারণেই ছড়ানো হোক না কেন, ফেক নিউজ বা গুজব অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেকোনো আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের মধ্যে দু-একটা ভুয়া খবর ভাইরাল হওয়া এখন আর নতুন কিছু নয়।
বর্তমানে সাধারণত ছবি এডিট করে অহরহ গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। মূলধারার গণমাধ্যমের ফটোকার্ড নকল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় হামেশা। অনেক সময় আসল ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান যোগ করে ছবির পটভূমি বদলে ফেলা হয়। জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, এমন বিষয়বস্তু নিয়ে মিথ্যা ও চটকদার ভিডিও তৈরি করে গুজব ছড়ানো হয়।
এ ছাড়া পুরোনো ভিডিওতে বর্তমান সময়ের কথা ব্যবহার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে একজনের চেহারায় তার আর্টিফিশিয়াল ভয়েস যুক্ত করে ডিপ ফেক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভুয়া ভিডিও তৈরি করে গুজব ছড়ানো হয়।
মূলধারার গণমাধ্যম থেকে কাল্পনিক উদ্ধৃতি, সত্য খবর পাল্টে ফেলা, অখ্যাত গণমাধ্যম বা ব্লগের খবর ব্যবহার করে বা কোনো গবেষণার ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যা ও অকার্যকর তুলনার মাধ্যমেও গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে।
গুজব ছড়িয়ে কারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, তা বোঝার আগেই ঘটনার শিকার হতে হয় গুজবের ফাঁদে পা দেওয়া মানুষদের। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, গুজবে বিশ্বাস করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কারণ, মানুষের মনের একটি অংশই চায় নেতিবাচক খবর বা গুজবে বিশ্বাস করতে।
ড. পল জোসেফ গোয়েবলস, নাৎসি জার্মানির তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘আপনি যদি একটা মিথ্যা বলেন এবং সেটা বারবার সবার সামনে বলতে থাকেন, তাহলে লোকজন একসময় সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করবে।’
প্রাচীনকালে মুখে মুখে গুজব ছড়ানো হতো। তারপর ছাপাখানার আবিষ্কার, প্রিন্ট মাধ্যমের আগমন এবং সংবাদপত্রের প্রচলনের মাধ্যমে গণমাধ্যম হয়ে ওঠে গুজব ছড়ানোর হাতিয়ার। কালের পরিক্রমায় ইন্টারনেট তথা সোশ্যাল মিডিয়ার সময় এর বিস্ফোরণ ঘটে ব্যাপকভাবে। যার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে জনজীবনে। গণমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা ও প্রভাব সম্পর্কে তাই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। গুজব প্রতিরোধে সরকার, জনসাধারণ ও গণমাধ্যমগুলোকে একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে।
গুজব শনাক্তকরণে গণমাধ্যমগুলোর নিজস্ব ফ্যাক্টচেকার থাকা দরকার। বিকল্প উৎস হতে তথ্য যাচাই, গুজবের বিপরীতে প্রকৃত তথ্য প্রচার করে গণমাধ্যম গুজবকে প্রতিহত করতে পারে। গুজব প্রতিরোধে আরও একটি কার্যকর উপায় হলো মিডিয়া লিটারেসি বা গণমাধ্যম সাক্ষরতা। যার ফলে একজন পাঠক বা দর্শক গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে এবং সহজেই প্রকৃত সংবাদ ও গুজবকে আলাদা করতে পারবে।
সরকারের আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি গুজব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যের ফ্যাক্টচেকিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার, গুজব শনাক্তে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গুজব সৃষ্টিকারীকে শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে গুজব অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।