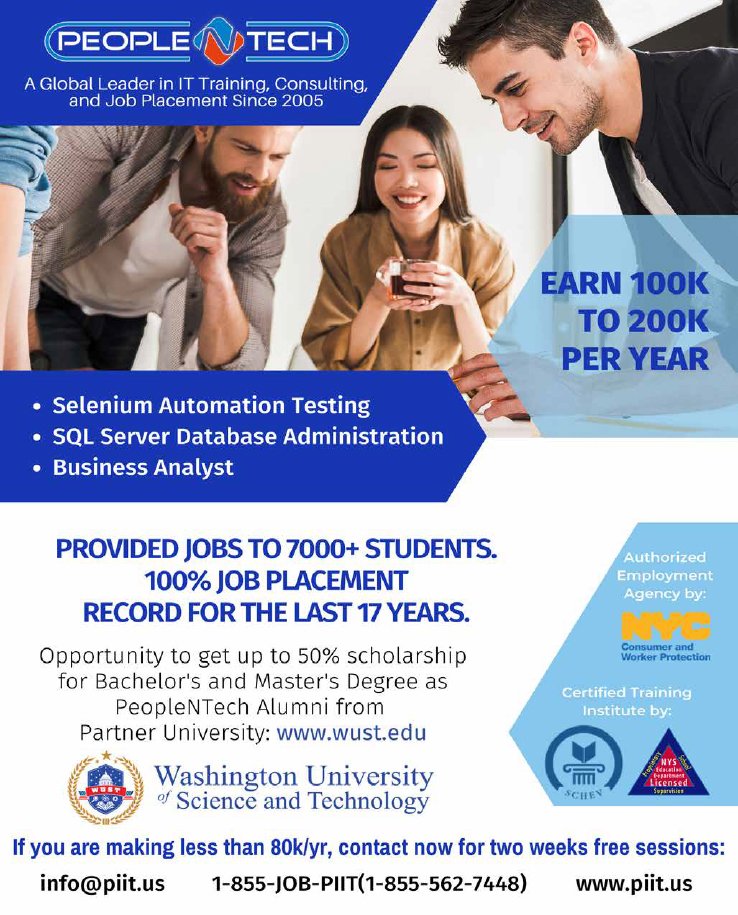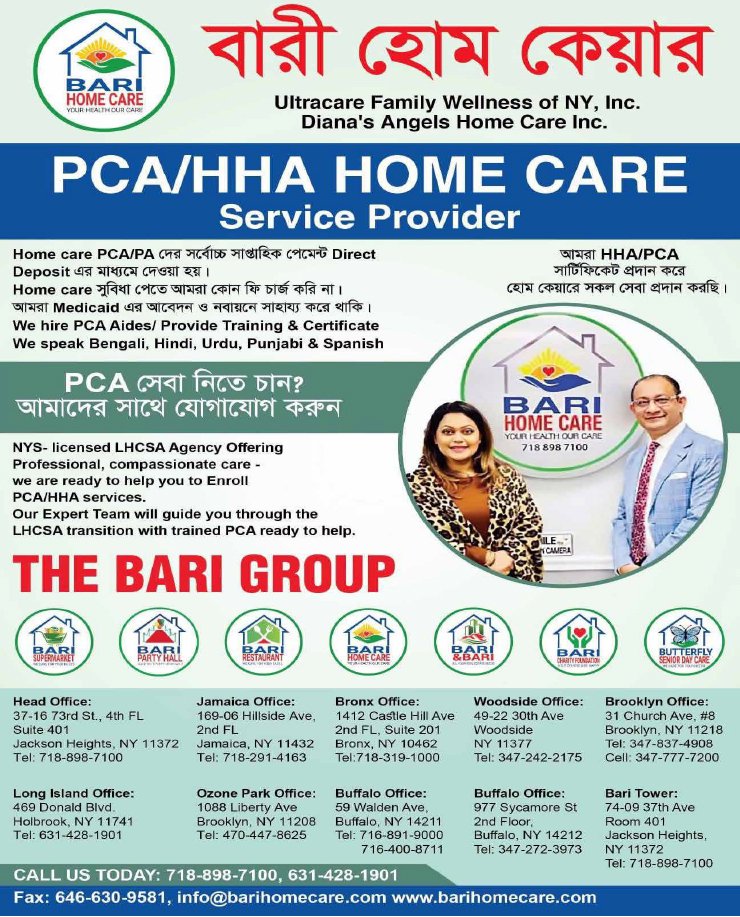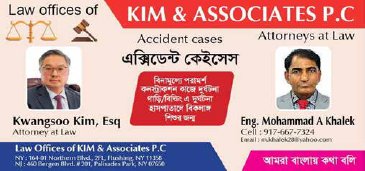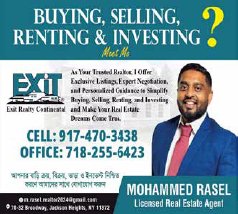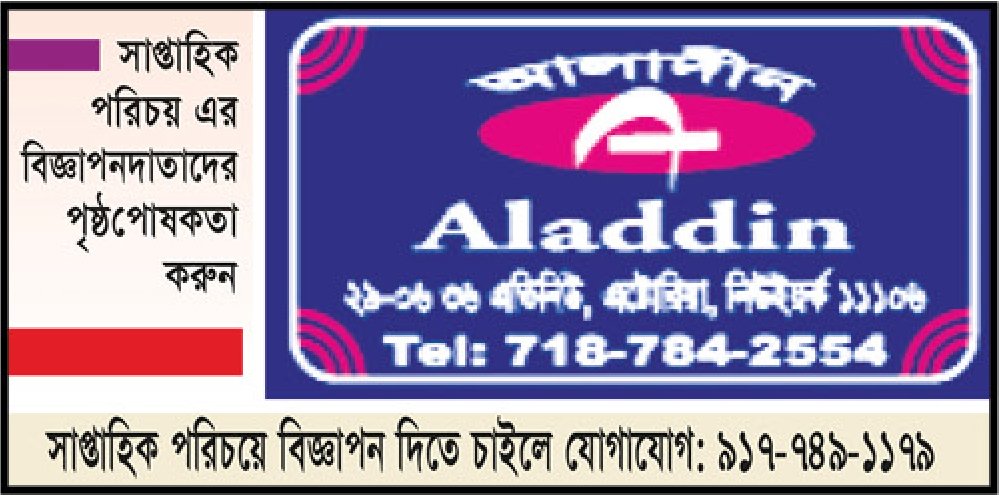

মহাভারতের চরিত্রগুলোর মধ্যে সর্বদাই একটি বিতর্ক বিদ্যমান—কে সর্বশ্রেষ্ঠ? কেউ খুঁজে পান অর্জুনের অতুলনীয় বীরত্বে, কেউ কর্ণের করুণা ও আত্মত্যাগে, আবার কেউ যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিরপেক্ষতায়। তবে বহু জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত একমত হন একটি অপ্রত্যাশিত নামে: বিদুর। কেন বিদুর? কারণ তার শক্তি এসেছিল তলোয়ার বা গদা থেকে নয়, বরং তার নৈতিক সাহস থেকে। তিনি ছিলেন সেই বিরল মানুষ, যিনি ‘ঠিককে ঠিক, আর ভুলকে ভুল বলার’ জন্য ভয় পাননি; যিনি সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি। বিদুর প্রমাণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের চেয়ে রাজসভায় নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা আরও কঠিন, আরও জরুরি।
এই বিদুরায়নই আজকের সমাজে সবচেয়ে অপ্রচলিত দক্ষতা। আমাদের মনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রশ্ন জন্ম নেয়—অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো প্রকাশের আগেই গলা টিপে মারা হয়। কেন? ভয়ে। ভয়ের সেই সংস্কৃতি এতটাই বিস্তৃত যে তা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গ্রাস করেছে। প্রশ্ন করলে সাংসারিক শান্তি ভঙ্গ হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে বসের কোপে চাকরি যেতে পারে কিংবা সরকার বা ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়ে নিরাপত্তা ও শান্তি নামক মরীচিকাটি এক লহমায় বিলীন হয়ে যেতে পারে। প্রশাসনিক ভ্রু কুঁচকে দেখলে কিংবা পুলিশি নজরদারি বাড়লে, একটা নীরব বার্তা দেওয়া হয়—প্রশ্ন নয়, নীরবতা শ্রেয়। এই ভয় কিছু হারানোর; তা জীবিকা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মমর্যাদা যাই হোক না কেন।
প্রশ্ন না করার এই অভ্যাস সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় অর্থনীতির মতো সংবেদনশীল খাতে। দেশের লাখ লাখ বেকার যুবক প্রতি বছর চাকরির জন্য হাহাকার করে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর চাকরির বাজারে আসা ১৫ লাখেররও বেশি যুবকের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি না: কেন বছরে অন্তত ১০ লাখ বেকারের চাকরি হলো না? কেন চাকরির সঠিক পরিসংখ্যান নেই?
সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যা জানানো হলেও, সেই তথ্য যাচাই করার বা সে সম্পর্কে আরও গভীর প্রশ্ন করার সাহস দেখানোর স্পর্ধা আমরা দেখাচ্ছি না। বেকারত্ব শুধু একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি জাতীয় সংকট, যার মূলোৎপাটন প্রশ্নের মাধ্যমেই সম্ভব।
একইভাবে, মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেও আমাদের প্রশ্ন ভোঁতা হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগ ও ঘোষণা সত্ত্বেও চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কেন কমছে না? এর সপক্ষে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা ডলার সংকটের মতো যুক্তি দেখানো হয়, তখন আমরা প্রশ্ন করি না: আন্তর্জাতিক বাজারে যখন দাম কমে, তখন কি সেই সুফল দেশে আসে? ডলার সংকটের আসল কারণ কী? এর পেছনে আর্থিক অব্যবস্থাপনা কতটা দায়ী?
এসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট, যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রায়শই অধরা থেকে যায়। যখন দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য চালু টিসিবি’র পণ্য বিক্রি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা সরকারের কাছে জবাব চাই না কেন এই অপরিহার্য পরিষেবাটি বন্ধ হলো? দারিদ্র্যসীমা ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও যদি আমরা প্রশ্ন না করি, তবে আমরা কোন ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি?
সাম্প্রতিক সময়ে, আমাদের প্রশ্নের ধার আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে যখন দেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার বা পরিবর্তনকালীন প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রত্যাশা ছিল—অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থায়, প্রশাসনে, ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বড় ধরনের সংস্কার আসবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে: কোন কোন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সংস্কার হয়েছে? কতটুকু হয়েছে? কেন প্রশাসন ও বিচার বিভাগে স্থবিরতা কাটছে না? কেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আশানুরূপ উন্নত হচ্ছে না?
এই সমস্ত কিছুই এখন রাজনীতির পর্যায়ে নেমে এসেছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি—সবই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। আর সেই সিদ্ধান্তগুলোর কৈফিয়ত চাওয়ার সময় এসেছে।
একটি দেশের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাসন, আর কর্মসংস্থান। অথচ সেই খাতগুলোতে অর্থ বরাদ্দের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই অপ্রয়োজনীয় বিলাসী সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রবণতা। সরকারের প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের কাছ থেকে ২০টি যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে বিতর্কের জন্ম দেয়। যখন দেশের শিক্ষায় যথেষ্ট বাজেট নেই, স্বাস্থ্যখাত নড়বড়ে, মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, এবং কর্মসংস্থান খাত ধুঁকছে— তখন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক প্রদর্শনে ব্যয় করার যৌক্তিকতা কী? এই যুদ্ধবিমান দিয়ে বাংলাদেশ কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? আঞ্চলিক সামরিক পরাশক্তি, যেমন ভারতের সামরিক সক্ষমতার সঙ্গে কি এই পদক্ষেপ তুলনীয়?
ভারত সামরিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বের চতুর্থ স্থানে। তাদের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতার কোনো বাস্তব ভিত্তি বাংলাদেশের নেই। তাহলে কেন এই সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়? এটি কি নিছকই জাতীয় ফুটানি বা রাজনৈতিক প্রেস্টিজ রক্ষার একটি চেষ্টা?
অন্যদিকে, যখন মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, যেমন আরকান আর্মি বা আরসা, বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবহার করে নিজেদের যুদ্ধ চালাচ্ছে, আমাদের ভূমি ব্যবহার করে চিকিৎসা কেন্দ্র বানাচ্ছে—তখন এই আকাশ থেকে আক্রমণকারী যুদ্ধবিমানের ভূমিকা কোথায়? সবার আগে প্রয়োজন ছিল সীমান্ত সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, যেখানে সরকার প্রায়শই নীরব। এই পরিস্থিতিতে ‘গরিবের টাকায় ফুটানি’ দেখানোর এই প্রবণতা কি গুরুতর অন্যায় নয়?
যখনই সরকার বা ক্ষমতাশীলদের এই প্রশ্নগুলো করা হয়, তখনই একটি সুপরিচিত কৌশল ব্যবহার করা হয়: ‘হোয়াটএবাউটজম’ (Whataboutism) বা ‘আগের সরকার কী করেছিল?’ এর মাধ্যমে প্রশ্নকর্তার মনোযোগ বর্তমান সমস্যা থেকে অতীতের লুটপাট বা ব্যর্থতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।
ক্ষমতাশীলরা সোজা উত্তর দেন না। তাঁরা বরং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তাঁরা যা করছেন সেটাই অনেক; তাঁরা যেন দেশবাসীর উপর দয়া করছেন। যুক্তি সাজাতে গেলে তাঁরা আগের সরকারের সঙ্গে তুলনা টানেন এবং বলেন, “আগে ওদের জিজ্ঞেস করে এসো, তখন দেশে অবাধ লুটপাট কেন হয়েছিল?”
কিন্তু এই কৌশল গণতন্ত্রে অচল। প্রশ্ন করতে হবে তাঁকেই, যিনি বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন। এই মুহূর্তে দেশের প্রজাতন্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মূল ফারাক এখানেই।
প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ককে সাধারণ মানুষ নির্বাচিত করে। গণতন্ত্রে আমজনতাই শেষ কথা। তারাই শাসক, তারাই পরিচালক। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্র হল একটি ‘ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিক’ বা সাধারণতান্ত্রিক গণতন্ত্র। অর্থাৎ, জনতা যেমন রাষ্ট্রনায়ক বাছবে, তেমনি তাঁর থেকে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকারও জনতাকেই দিয়েছে সংবিধান। প্রজাতন্ত্রের কোনও সরকার কোনও একনায়কের তল্পিবাহক নয়; তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ও সেবক।
অতএব, যখন জনগণ আওয়ামী লীগের ওপর বিরক্ত হয়েই পরিবর্তন চেয়েছিল, তখন নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন। জনগণের সমর্থন মানে অতীতের ব্যর্থতার অজুহাত দেখিয়ে চোখ উল্টে থাকা নয়। যদি লুটপাট বন্ধ করতে না পারার জন্য অতীতের সরকার দায়ী হয়, তাহলে বর্তমান সরকারেরও হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অধিকার নেই। প্রশ্ন তো বর্তমান সরকারকেই করতে হবে, কারণ ক্ষমতায় তাঁরাই আছেন।
অথচ, এতকিছুর পরেও যখন প্রশ্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে আন্তর্জাতিক সূচকে আমাদের দেশকে নিচের দিকে থাকতে হয়। বাক্স্বাধীনতায় কেন আমাদের স্থান পেছনের সারিতে? এর উত্তর কি আমরা সরকারের কাছে চাইতে পারব না?
আইনের ফাঁক বা রাজরোষ হয়তো কিছুদিনের জন্য আমজনতাকে থামিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গতি প্রমাণ করে—এই নীরবতা স্থায়ী হয় না। আজ না হয় কাল, মানুষ প্রশ্ন করবেই। সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে, তা প্রয়োগ না করাটাই বরং অসাংবিধানিক।
বিদুর হওয়ার জন্য যোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু সাহস বা ‘বুকের খাঁচাটুকু’। অন্যায়কে সমর্থন না করে যা সঠিক, তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখানোর চেয়ে সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখানো অধিক জরুরি।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হলো প্রশ্ন করা। প্রশ্নই হল জবাবদিহিতার ভিত্তি, আর জবাবদিহিতাই সুশাসনের চাবিকাঠি। যেদিন দেশের প্রতিটি নাগরিক ভয়কে জয় করে বিদুরের মতো প্রশ্ন করতে শিখবে, সেদিনই প্রকৃত অর্থে দেশে সুশাসন ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। প্রশ্ন করার এই সংস্কৃতিই আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একমাত্র সুরক্ষা কবচ।