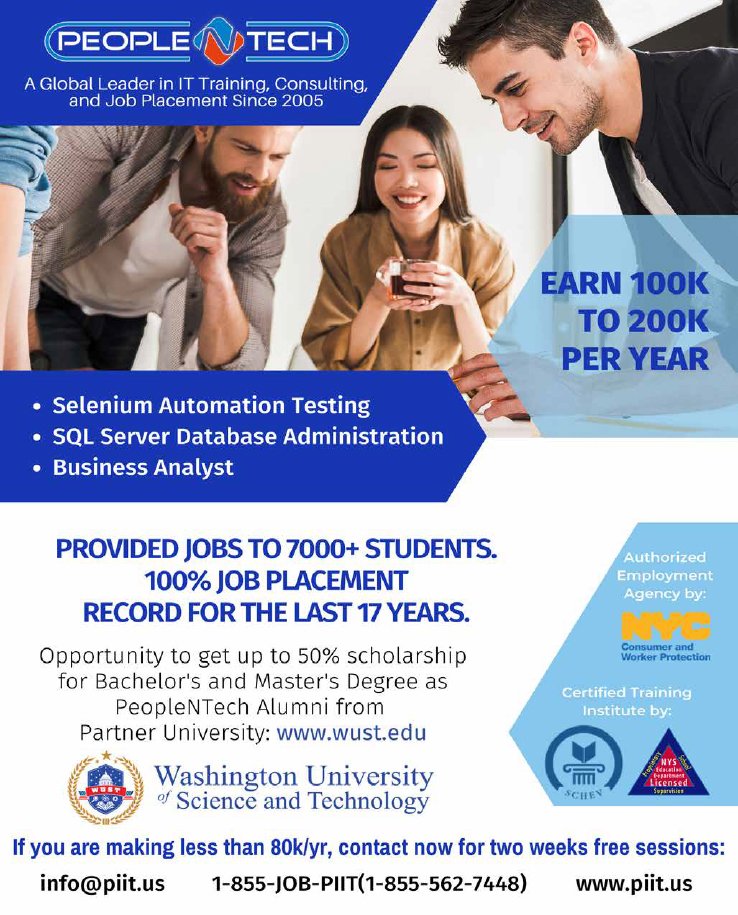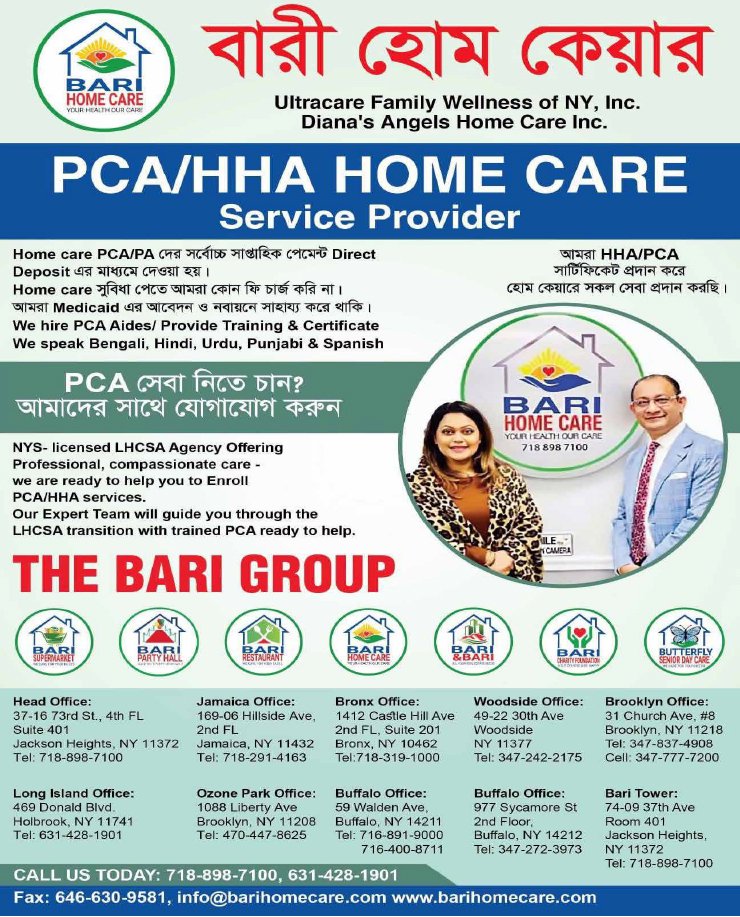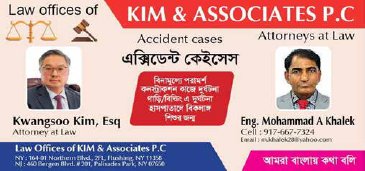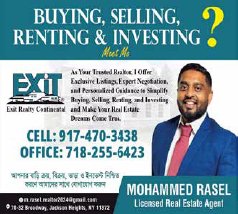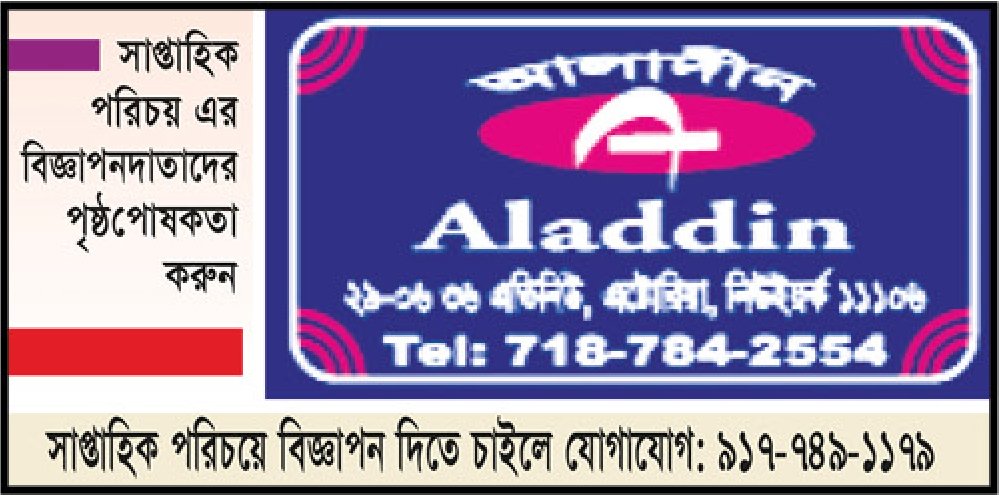
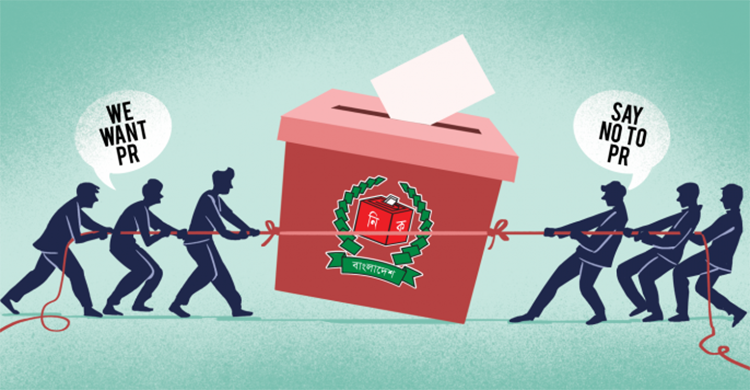
বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। বিদ্যমান “প্রথম-হওয়া-জয়ী” (First Past the Post) ভোট পদ্ধতি প্রায়শই বাস্তব ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসন বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেক সময় ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ সংসদে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব পায় না। এই বাস্তবতায় বর্তমানে বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের আওতায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) ভোট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসন বণ্টন করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের প্রকৃত ভোটশক্তি অনুযায়ী সংসদে প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতির প্রবর্তন গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করতে পারে। তবে এর সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও জড়িত রয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা, দলীয় শৃঙ্খলা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক জটিলতা। তবে রাজনৈতিক বহুমতকে সম্মান জানিয়ে অংশীদারিত্বমূলক রাজনীতি বিকশিত না হলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং দেশের বাস্তবতার সঙ্গে তা খাপ খাওয়ানো অপরিহার্য। এই বিষয়ের মূল ধারণাগুলি বুঝার সুবিধার্থে, লেখার মধ্যে কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
পিআর পদ্ধতির মৌলিক ধারণা : • ভোটের Proportionate (PR) পদ্ধতি বা Proportional Representation (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা) হলো এমন একটি ভোট পদ্ধতি, যেখানে নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পায়, সংসদ বা নির্বাচিত আসনে তাদের সেই অনুপাতে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। সাধারণত First Past the Post (FPTP) বা সর্বাধিক ভোটে বিজয়ী পদ্ধতিতে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, সে একক আসনে জিতে যায়। এখানে মোট ভোটের অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব হয় না। কিন্তু PR পদ্ধতিতে, একটি দলের পাওয়া মোট ভোটের শতাংশের সাথে সংসদে তাদের আসনের সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ধরা যাক একটি সংসদে মোট ১০০টি আসন আছে। নির্বাচনে, লাল দল পেয়েছে ৪০% ভোট তারা আসন পাবে ৪০ টি। সবুজ দল পেয়েছে ৩৫% ভোট তারা আসন পাবে ৩৫ টি। নীল দল পেয়েছে ১৫% ভোট তারা আসন পাবে ১৫ টি। সাদা দল পেয়েছে ১০ % ভোট এবং তারা আসন পাবে ১০ টি। অর্থাৎ, ভোটের পাওয়ার অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন হবে। পিআর পদ্ধতির ভোটকে আসনে রূপান্তরের সময় জনগণের মোট মতামতকে প্রতিফলিত করে। এজন্য একে অনেক বিশেষজ্ঞ এই পদ্ধতিকে “ন্যায্য প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি” বলে থাকেন। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন: ১) পার্টি লিস্ট পদ্ধতি বা Party List PR:
এটি পি আর-এর সবচেয়ে প্রচলিত ধরন। এখানে ভোটাররা সরাসরি কোনো প্রার্থীকে নয়, বরং একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল একটি প্রার্থীর তালিকা (Party List) জমা দেয়। নির্বাচন শেষে প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন পায় এবং তালিকা থেকে প্রার্থীরা সংসদে যায়। পার্টি লিস্ট পদ্ধতির আবার দুটি ধরন আছে: ক) বন্ধ তালিকা বা Closed List ঃ ভোটার কেবল দলকে ভোট দিতে পারে, তালিকার ক্রম ঠিক করে দল। যেমন, লাল দল যদি ২০% ভোট পায়, আর সংসদে ৩০০ আসন থাকে, তবে তারা ৬০ আসন পাবে। এই ৬০ জন প্রার্থী যাবে লাল দলের আগেই নির্ধারিত তালিকা থেকে। ফলে পদ্ধতিটি সহজ এবং ভোটগণনা দ্রুত হয়। তবে প্রার্থী নির্বাচনে দলীয় নেতৃত্বের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে, জনগণের প্রার্থীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। খ) Open List (উন্মুক্ত তালিকা)ঃ ভোটার কেবল দলকে নয়, তালিকার ভেতর কোন প্রার্থীরা সংসদে যাবে, তাও নির্ধারণ করতে পারে। এতে ভোটারদের ক্ষমতা বাড়ে, কারণ তারা দলীয় তালিকার ভেতর থেকেও পছন্দ প্রকাশ করতে পারে। ফিনল্যান্ড এবং ব্রাজিল-এ এই পদ্ধতি চালু আছে। গ) স্থানান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতি বা Single Transferable Vote (STV)ঃ এটি একটি অপেক্ষাকৃত জটিল কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখানে ভোটাররা প্রার্থীদের পছন্দের ক্রমে (১, ২, ৩ ইত্যাদি) ভোট দেন। একটি প্রার্থী নির্বাচিত হতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট (quota) পেতে হয়। যদি কোনো প্রার্থী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোট পায়, তাহলে অতিরিক্ত ভোট অন্য প্রার্থীর কাছে স্থানান্তরিত হয়। ইউরোপের আয়ারল্যান্ড এবং মাল্টায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে ভোটগণনা অনেক জটিল। ঘ) মিশ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা বা Mixed Member Proportional (MMP)ঃ এটি একটি মিশ্র ব্যবস্থা—এখানে FPTP এবং PR উভয়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়। সংসদের অর্ধেক আসন নির্ধারিত হয় সরাসরি ভোটে (FPTP)। বাকি অর্ধেক আসন দেওয়া হয় PR পদ্ধতিতে, জাতীয়ভাবে মোট ভোটের অনুপাতে। তবে কোন কোন আসনে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সেটা আগে থেকেই বলা হয়। এর ফলে বড় দল যেমন সরাসরি আসন জেতে, ছোট দলগুলোও PR আসনের মাধ্যমে সংসদে প্রবেশের সুযোগ পায়। জার্মানি এবং নিউজিল্যান্ড এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর ফলে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়।
• আসন বণ্টনের গাণিতিক সূত্র: পিআর পদ্ধতিতে ভোটকে আসনে রূপান্তর করতে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র (seat allocation formulas) ব্যবহার করা হয়। এগুলির কারণে সংসদের গঠন সামান্য ভিন্ন হতে পারে। যেমন- ১) D’Hondt পদ্ধতি ২) Sainte-Laguë পদ্ধতি ৩) Largest Remainder পদ্ধতি (Hare বা Droop Quota) ।
বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনি প্রেক্ষাপট : • বাংলাদেশে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় FPTP-এর প্রভাব বিদ্যমান। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মোট ৩০০টি সাধারণ আসনে ভোট হয়। এখানে ব্যবহার করা হয় First Past the Post (FPTP) বা সর্বাধিক ভোটে জয়ী হওয়ার পদ্ধতি। কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট আসনে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভোট পেলেই জয়ী হবে, এমনকি তার ভোট মোট ভোটের অর্ধেকেরও কম হলেও। এতে বড় দলগুলো ব্যাপকভাবে সুবিধা পায়, কারণ তারা সারা দেশে প্রার্থীদের দাঁড় করাতে পারে এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভোটেও আসন জয় করে।
• বড় দলগুলি জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত সংগঠন রাখে। ভোট যদি সমানভাবে কিছুটা বেশি পায়, FPTP পদ্ধতিতে বিপুল আসন পেয়ে যায়। ফলে তারা এককভাবে সরকার গঠন করতে পারে। ছোট দলগুলি যদিও তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভোট পায়, কিন্তু সারা দেশে ছড়িয়ে না থাকায় আসনে রূপান্তরিত করতে পারে না। অনেক সময় বড় দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে টিকে থাকতে হয়। FPTP তাদের প্রতিনিধিত্ব সীমিত করে, ফলে নীতিনির্ধারণে প্রভাবও কমে যায়। এই কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি কার্যত দ্বিদলীয় কাঠামো (AL vs BNP) তে আটকে আছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হতে পারে।
• FPTP-এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো “ভোট অপচয়” । কোনো আসনে যদি জয়ী প্রার্থী ৪০% ভোট পান, তবে বাকি ৬০% ভোট কার্যত হারিয়ে যায়। সেই আসনের নির্বাচিত এমপি শুধু নিজের ভোটারদের নয়, পুরো এলাকার প্রতিনিধি, কিন্তু বাস্তবে অর্ধেকেরও বেশি মানুষের ভোট অপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে পড়ে। এতে ভোটারদের মধ্যে হতাশা ও বিমুখতা জন্মায়—“আমাদের ভোট দিলেও লাভ নেই।”
পি আর পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা : • সুবিধা- ১) ন্যায্য প্রতিনিধিত্বঃ FPTP পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী ৩৫–৪০% ভোট পেলেও বাকিদের ভোট “অপচয়” হয়ে যায়। পি আর পদ্ধতিতে প্রতিটি দলের মোট প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন ভাগ হয়। এতে ভোটারদের প্রকৃত মতামত সংসদে প্রতিফলিত হয়। একটি দল যদি জাতীয় ভোটে ২০% পায়, সংসদেও প্রায় ২০% আসন পাবে। ২) ভোট অপচয় হ্রাসঃ FPTP–তে হেরে যাওয়া প্রার্থীর সব ভোট বাদ পড়ে যায়। পিআর–এ হেরে গেলেও সেই ভোট দলীয় মোট ভোটে যোগ হয় এবং তালিকা–আসনের মাধ্যমে সংসদে প্রভাব ফেলে। এতে ভোটাররা মনে করেন—“আমার ভোট হারাল না”—ফলে ভোটদানে উৎসাহ বাড়ে। ৩) ছোট দল ও নতুন রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ- বড় দলগুলো এককভাবে আসন দখল করতে পারে না। ছোট দলগুলোও জাতীয় ভোটের ভিত্তিতে সংসদে প্রবেশ করতে পারে। এতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি, বিকল্প নেতৃত্ব ও তরুণদের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বাড়ে। যেমন নেপালে পি আর চালুর ফলে বিভিন্ন নতুন দল সংসদে জায়গা পায়। ৪) রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি : বিভিন্ন মতাদর্শ, অঞ্চল, সংখ্যালঘু, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী—সবাই সংসদে কণ্ঠ পায়। তালিকা–ভিত্তিক আসনে কোটা দিয়ে নারী ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সহজ হয়। এতে গণতন্ত্র আরও অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।
• অসুবিধা- ১) বহুদলীয় সংসদ বা জোট-রাজনীতির অস্থিরতা : পি আর–এ বেশি দল সংসদে প্রবেশ করে, এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। ফলে সরকার গঠনের জন্য জোট দরকার হয়। এতে জোট ভাঙা-গড়া চলতে থাকে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে।২) দলীয় নেতৃত্বের আধিপত্য : তালিকা–ভিত্তিক আসন বণ্টন অনেকাংশে দলীয় প্রধান বা কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করে। এতে স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ কমে যায়। দলীয় প্রধান চাইলে নিজের ঘনিষ্ঠদের তালিকায় বসাতে পারেন, “পৃষ্ঠপোষকতা” রাজনীতি বাড়তে পারে। ৩) এলাকা-ভিত্তিক জবাবদিহিতা দুর্বল হওয়া- FPTP–তে এমপি নির্বাচিত হন সরাসরি এলাকার ভোটারদের দ্বারা এবং তাদের কাছে তিনি জবাবদিহি করেন। PR–এ যদি কেবল তালিকা–ভিত্তিক এমপি আসেন, তবে তারা স্থানীয় ভোটারের কাছে দায়বদ্ধতা অনুভব নাও করতে পারেন। এতে এলাকায় সরাসরি যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের চাপ কমতে পারে। ৪) ভোটগণনা ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা : FPTP বেশী সহজ অর্থাৎ যে বেশি ভোট পেল- সেই জয়ী। PR–এ আসন বণ্টন করতে হয় জটিল গাণিতিক সূত্রে (D’Hondt, Sainte-Laguë, Hare quota ইত্যাদি)। এতে সময় বেশি লাগে, নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক চাপ বাড়ে। বাংলাদেশে যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে বিভ্রান্তি বা অনিয়মের ঝুঁকি থাকতে পারে।
পিআর পদ্ধতি গ্রহণে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি পিআর–এর সাফল্য কাগজে নয়—ব্যবস্থাপনায়। তাই প্রয়োগের পূর্বেই কয়েকটি প্রশাসনিক এবং আইনগত বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। যেমন:
• আইনে বা সংবিধানে মিশ্র পদ্ধতির স্বীকৃতি (PR বা MMP/Parallel) করতে হবে। নির্বাচন আইনে তালিকা–জমা, থ্রেশহোল্ড, আসন-ফর্মুলা, কোয়ালিশন রুলস ইত্যাদি লিখিত করে নিতে হবে।
• নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা (Election Management Capacity) বাড়াতে হবে। ফল গণনা, ফর্মুলা প্রয়োগ, হিসাব—অটোমেশন করতে হবে । সব পর্যায়ে ট্রেনিং দিতে হবে যেমন, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের—FPTP–র পাশাপাশি PR গণনার মডিউল জানা থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তালিকা/ফর্মুলা/বণ্টন ইত্যাদি যাচাইযোগ্য ডেটা–রিলিজের প্রযুক্তি ঠিক করতে হবে।
• ব্যালট ডিজাইন ও ভোটার শিক্ষা দিতে হবে যেমন, দুটি ভোট: ক) এলাকাভিত্তিক প্রার্থী (FPTP), খ) দলীয় তালিকা (PR)। ব্যালট স্পষ্ট, প্রতীকে সামঞ্জস্য করতে হবে যেন গ্রামের ভোটারও বুঝতে পারে। প্রয়োজনে মক ব্যালট দিয়ে নাগরিক শিক্ষা ক্যাম্পেইন করতে হবে। মিডিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এইগুলি ব্যাপক প্রচার করতে হবে যেমন- কেন দুটো ভোট? এতে আপনার লাভ কী? ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জনগণকে দিতে হবেনগণ।
• পার্টির অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র সংস্কার করতে হবে। যেমন, তালিকা কারা করবে? একই সাথে পার্টির সংবিধানে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। পার্টির লিডারশিপ এবং পাওয়ার প্লে, জেন্ডার/মাইনরিটি কোটার কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।
• পিআর পদ্ধতির একটা টেস্ট বা পাইলট প্রজেক্ট ১–২টি সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/জেলা পর্যায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এই পদ্ধতির সুবিধা-আসুবিধাগুলি যাচাই করে নিতে হবে। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা
• জার্মানি: জার্মানিতে Mixed Member Proportional (MMP) পদ্ধতিতে ভোট হয়। ভোটার দুটি ভোট দেয়:
একটি এলাকার প্রার্থীকে (FPTP) এবং অন্যটি দলীয় তালিকাকে (PR) । FPTP আর PR মিলিয়ে মোট আসন দলীয় ভোটের অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। ফলে প্রতিনিধিত্ব ন্যায্য হয়, ছোট দলও সংসদে আসতে পারে। আবার বড় দলগুলোকেও আসন বাড়তি মেলে না এবং এককভাবে আধিপত্য থাকে না।
• ইসরায়েল: ইসরাইলে Pure PR (শুদ্ধ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) অনুযায়ী ভোট হয়। যেমন, পুরো দেশকে একটিমাত্র আসন–এলাকা ধরা হয়। দলগুলো জাতীয় ভোট পায়, আর ১%–৩% ভোট পেলেই সংসদে ঢুকতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দল সংসদে ঢোকে। কোনো দল কখনো এককভাবে সরকার গঠন করতে পারে না।
• নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন: ভোটাররা কেবল একটি দলকে ভোট দেয়। দল জাতীয়/আঞ্চলিক তালিকা দেয়, সেই তালিকা অনুযায়ী আসন বণ্টন হয়। ফলে, ছোট দলও সংসদে যায়, তবে Threshold (ন্যূনতম ভোটসীমা) থাকায় ভাঙন খুব বেশি হয় না। এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুব উন্নত, দলগুলো দায়িত্বশীল। তাই বহুদলীয় জোট সরকার হলেও স্থিতিশীল থাকে।
• দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটঃ ক) ভারতঃ ভারতে পুরোপুরি FPTP। এর ফলে বড় দল (BJP বা কংগ্রেস) বিপুল আসন পায়, যদিও জাতীয় ভোট ৩৫–৪০% এর বেশি হয় না। ছোট দলগুলোর ভোট অপচয় হয়। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সমস্যা দেখা দেয়। খ) পাকিস্তান : জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে FPTP, তবে সংরক্ষিত আসনে দলীয় ভোট অনুযায়ী PR বণ্টন হয় (নারী ও সংখ্যালঘু আসন) । এর ফলে আংশিক অন্তর্ভুক্তি এলেও মূল কাঠামো একচেটিয়া থাকে। গ) শ্রীলঙ্কাঃ FPTP এবং PR মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (প্রতিটি জেলার ভেতরে ভোটের অনুপাতে আসন বণ্টন)। এর ফলে ছোট দল কিছু আসন পায়, তবে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রবল। দক্ষিণ এশিয়ায় PR নিয়ে আলোচনা থাকলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্বল হওয়ায় পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির সম্ভাব্য প্রয়োগ এবং সুপারিশ
• বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন পুরোপুরি FPTP (First Past the Post) পদ্ধতিতে হয়। হঠাৎ পুরো দেশকে PR (Proportional Representation)–এ নেওয়া রাজনৈতিকভাবে কঠিন, কারণ বড় দলগুলো এতে আপত্তি তুলবে এবং প্রশাসনিক জটিলতাও থাকবে। তাই বাস্তবসম্মত প্রস্তাবনা হলো আংশিক PR বা Mixed System চালু করা। যেমন, মোট ৩০০ আসনের মধ্যে হয়তো ২০০ আসন FPTP-তে থাকবে, আর ১০০ আসন PR-এ যাবে। এতে বড় দলের আধিপত্য কিছুটা থাকবে, আবার ছোট দল ও নতুন শক্তিও সুযোগ পাবে। তবে এটি হবে ধাপে ধাপে-প্রথমে আংশিক, পরে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ PR এর দিকে যাওয়া যেতে পারে। তবে মডেলটির টেকসই কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই করতে হবে।
• পি আর পদ্ধতিতে অনেক ছোট দলও সংসদে ঢুকতে পারবে- এতে অন্তর্ভুক্তি (inclusion) বাড়বে। কিন্তু যদি খুব বেশি দল আসে, তাহলে সরকার চালানো কঠিন হবে (অস্থিরতা আসবে) ফলে স্থিতিশীলতা (stability) কমে যাবে। এই ভারসাম্য রাখতে কয়েকটি নিয়ম ব্যবহার করা যায়। যেমন, ক) ন্যূনতম ভোটসীমা- যদি কোনো দল জাতীয়ভাবে কমপক্ষে ৫% ভোট না পায়, তাহলে তারা সংসদে ঢুকতে পারবে না। এতে একেবারে ক্ষুদ্র দল বাদ পড়বে, সংসদে দল কম থাকবে এবং স্থিতিশীলতা থাকবে। খ) PR আসনে সিট-সাইজ PR আসন যদি খুব বড় হয় (যেমন ১৫ আসনের তালিকা), তাহলে ছোট দল সহজে ঢুকবে। আর যদি ছোট হয় (যেমন ৩–৪ আসনের তালিকা), তবে বড় দলের সুবিধা থাকবে। ধরা যাক, ঢাকা বিভাগে ১০টি PR আসন রাখা হলো। ভোট গণনায় দেখা গেল লাল দল পেয়েছে ৫০% ভোট, সবুজ দল পেয়েছে ৩০% ভোট, নীল দল পেয়েছে ১৫% ভোট এবন সাদা দল পেয়েছে ৫% ভোট। এখন মোট আসন বণ্টন হবে (মোট আসন ১০)ঃ লাল দল ৫০% ভোট = ৫ আসন, সবুজ দল ৩০% ভোট = ৩ আসন, নীল দল ১৫% ভোট = ১.৫ ≈ ২ আসন এবং সাদা দল ৫% ভোট = ০.৫ ≈ আসন পাবে না (যদি ৫% threshold-এর নিচে ধরা হয়, অথবা rounding নিয়মে বাদ যায়)। এখন তালিকা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচিত হবে। যেমন- লাল দল তাদের জমা দেওয়া তালিকার প্রথম ৫ জনকে সংসদ সদস্য বানাবে। একই ভাবে সবুজ দল তালিকার প্রথম ৩ জনকে এবং নীল দল তাদের তালিকার প্রথম ২ জনকে সংসদ সদস্য বানাবে। বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক ৮–১০ আসনের তালিকা মাঝামাঝি একটি ভালো সমাধান হতে পারে যেটা অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতার ভারসাম্য রাখতে পারে। গ) আসন বণ্টন ফরমুলাঃ D’Hondt ফর্মুলা হতে পারে যেখানে বড় দলকে একটু বাড়তি সুবিধা দিয়ে সংসদে স্থিতিশীলতা বাড়ানো যাবে। ঘ) Sainte-Laguë ফর্মুলাঃ যেখানে ছোট দলকে বেশি সুযোগ দিবে এবং অন্তর্ভুক্তি বেশী হবে। বাংলাদেশে শুরুতে D’Hondt ব্যবহার করা যেতে, পরে চাইলে Sainte-Laguë- ফর্মুলাতে যাওয়া যেতে পারে।
• বর্তমানে বাংলাদেশে নারী আসন সংরক্ষিত (৫০ আসন), যা দলীয় আসনের অনুপাতে বণ্টিত হয়। এতে নারীরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় না, বরং দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে আসে এটিকে অনেকেই “টোকেন প্রতিনিধিত্ব” বলে মনে করেন। পিআর তালিকা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম ৩০–৪০% নারী রাখতে বাধ্য করা যায়। এতে নারীরা সরাসরি ভোটের ভিত্তিতে সংসদে আসতে পারবেন, সংরক্ষণের প্রয়োজন কমবে। এর ফলে নারীর নেতৃত্ব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ও মূলধারায় পরিণত হবে। রাজনীতিতে প্রকৃত নারীর ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান হবে।
• কোনো নির্বাচনি ব্যবস্থা একা সফল হয় না—রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিপক্ক না হলে PR ব্যর্থ হতে পারে। কারণ দলীয় নেতৃত্বে একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা, পার্টির ভেতরে গণতন্ত্রের অভাব, প্রতিপক্ষকে দমন করার সংস্কৃতি ইত্যাদি। যদি অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র চালু করা যায়, ভিন্নমতকে সহনশীলভাবে গ্রহণ করা এবং নির্বাচনকে ইঞ্জিনিয়ারিং না করে “অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা” হিসেবে দেখা হয় তাহলে এই নির্বাচন ফলপ্রসু হতে পারে বলে অনুমেয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত পরিপক্ব হবে, PR তত বেশি কার্যকর হবে।
• সংসদ ভাঙতে চাইলে শুধু “সরকার ফেলে দাও” বলা যাবে না এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটিও একসাথে বলতে হবে। এতে হুটহাট সরকার পতন হবে না ফলে স্থিতিশীলতা থাকবে।
বাংলাদেশের জন্য উপযোগী পদ্ধতি: সহজ কথায় অতিরিক্ত ছোট দল বাদ দিতে Threshold বা সর্বনিম্ন সীমা, বড় দলকে সামান্য বাড়তি সুবিধা দিতে D’Hondt, আর সরকার গঠনে স্বচ্ছ নিয়ম দিতে Investiture Rule( নতুন সরকার গঠনের আগে সংসদে সরাসরি আস্থা ভোট নিতে হবে—সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যে দল বা জোটকে সমর্থন করছে, কেবল তারাই সরকার গঠন করতে পারবে। এতে স্বচ্ছতা তৈরি হয়, জনগণ ও সংসদ উভয়ের কাছেই পরিষ্কার থাকে কে সরকার গঠন করছে, এবং দুর্বল বা অস্থিতিশীল সরকার হবার সম্ভাবনা কমে যায়।) এই তিন মিলিয়ে বাংলাদেশে পিআর চালু করলে অন্তর্ভুক্তি আর স্থিতিশীলতার মধ্যে ভালো ভারসাম্য পাওয়া যাবে। তবে যে পদ্ধতিই হোক না কেন সেটা যেন সবার জন্য উপযোগী হয় সেটা দেখতে হবে। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনগণের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে পাইলট প্রজেক্ট বা গবেষণার মাধ্যমে সার্বজনীন টেকসই পদ্ধতি বের করতে হবে।
PR বা মিশ্র ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হলে নির্বাচন কমিশনের (EC) সক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য কমিশনের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা। ব্যালট ডিজাইন, ভোট গণনা, আসন বণ্টন—এসব প্রযুক্তিগত দক্ষতা তৈরি করা। ফলাফল ঘোষণায় স্বচ্ছ সফ্টওয়্যার ও ডেটা-সিস্টেম ব্যবহার। পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল দেওয়া। সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়োগ ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। স্বার্থপর এবং অসৎ ব্যক্তিকে নিয়োগ পরিহার করতে হবে। যদি EC শক্তিশালী ও স্বচ্ছ না হয়, তবে PR সিস্টেম সহজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভোট পদ্ধতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক দলগুলোও তাদের যথাযথ অবস্থান পাবে, যা রাজনৈতিক বহুমতকে সম্মান জানাবে এবং সংসদকে প্রকৃত অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল করে তুলবে। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, আইনি কাঠামোর সংস্কার, নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের আস্থা অর্জন অপরিহার্য শর্ত।
বিশ্বের নানা দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সফলভাবে কার্যকর হলেও প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বাস্তবতা আলাদা। তাই বাংলাদেশে এ পদ্ধতির বাস্তবায়নে সরল নকলের পরিবর্তে একটি গবেষণাভিত্তিক, ধাপে ধাপে এবং দেশীয় বাস্তবতানির্ভর রূপান্তর প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভোট পদ্ধতি বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে আরও মজবুত, কার্যকর ও টেকসই করতে পারে।
রেফারেন্স
• Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Methuen.
• Norris, P. (2004). Electoral Engineering. Cambridge University Press.
• IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2021). Electoral System Design Database.
• Rahman, T. (2019). Parliamentary Democracy in Bangladesh. Dhaka University Press.
• Reilly, B. (2001). Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge University Press.
• D’Hondt, V. (1882). Système pratique et raisonné de représentation proportionnelle. Bruxelles.
• Sainte-Laguë, A. (1910). La représentation proportionnelle et la méthode des moindres carrés. Paris.
• IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm.
• Bundeswahlleiter (Federal Returning Officer, Germany). Official resources on the German Bundestag electoral system.
• Israeli Knesset. Electoral System Information. knesset.gov.il.
• Election Commission of India. Handbook on FPTP Electoral System in India.
• Election Commission of Pakistan. Reserved Seats and Proportional Representation Rules. লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা।