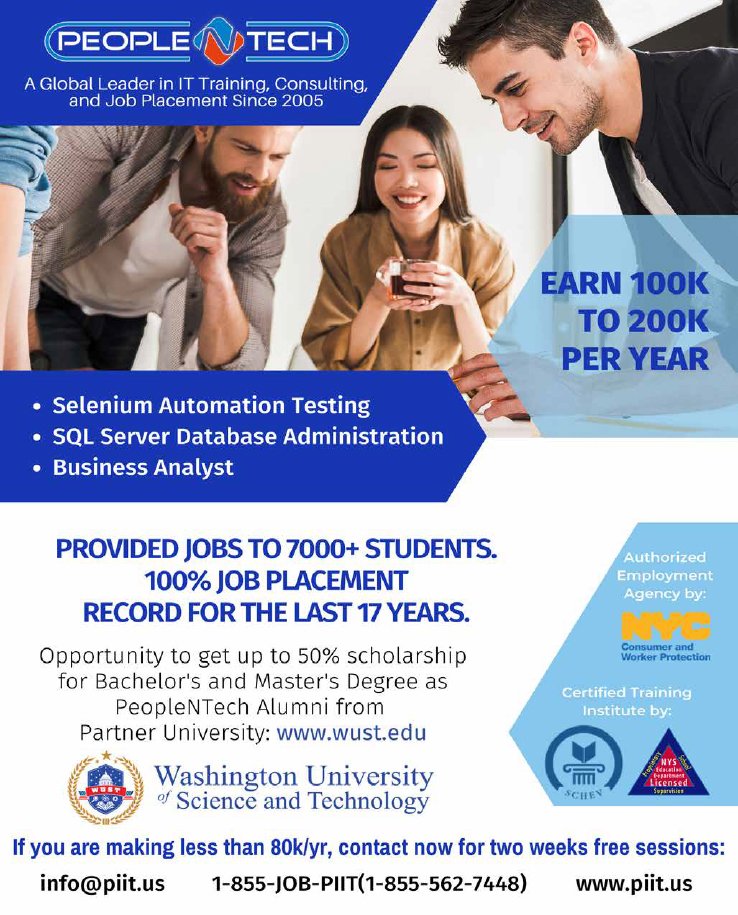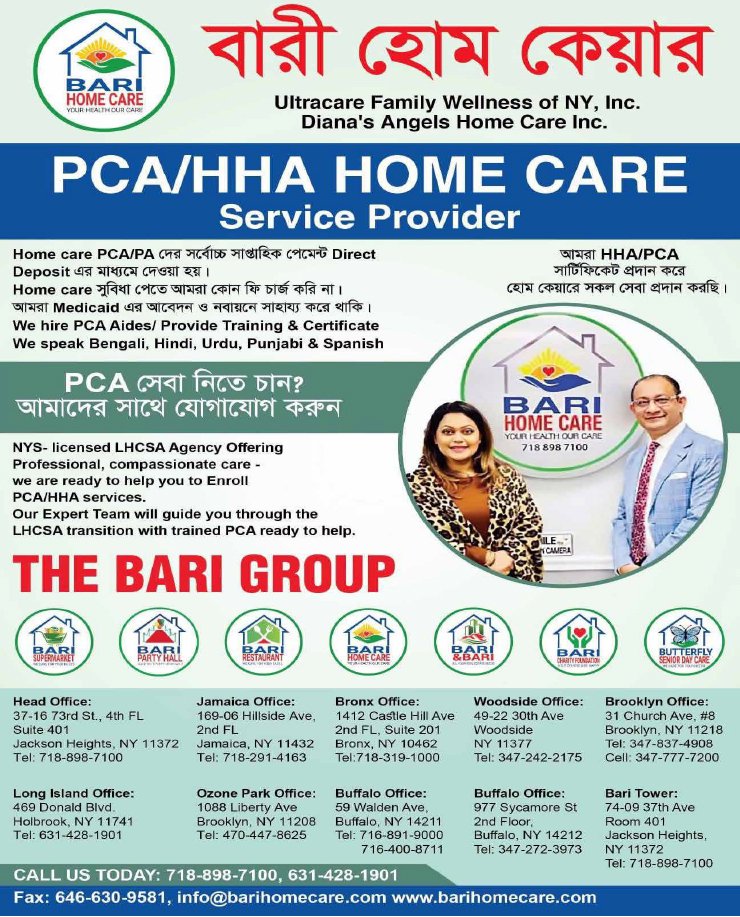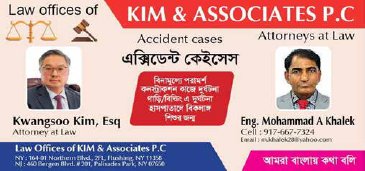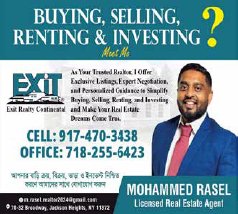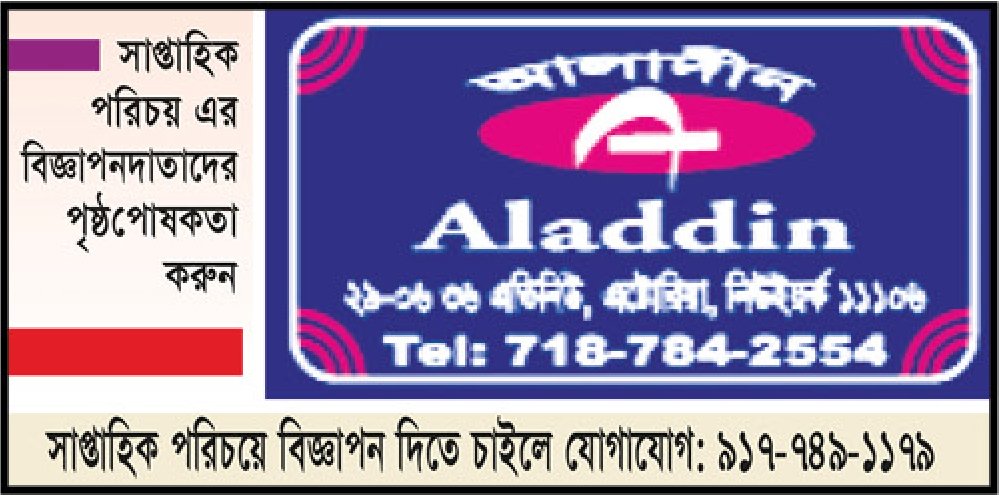

কিছুদিন আগে ‘অপজিশন ইন্টারন্যাশনাল’ নামে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাভিত্তিক এক এনজিওতে নাগরিক কোয়ালিশনের হয়ে মিটিং করি। ওই এনজিওর কাজ বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিতের জন্য প্রচারণা ও টেকনিক্যাল সাহায্য করা। কথা প্রসঙ্গে তারা আফসোস করছিল, এত টেকনোলজি নিয়ে এখনো কোনো দেশে সন্তোষজনকভাবে প্রবাসী ভোট চালু করতে পারেনি।
আমাদের দেশ সেই কঠিন পথে হাঁটা শুরু করল। আমাদের কমিশনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন দেশে শিক্ষাসফর করে কী শিখে আসছেন, তা আসলে সামনেই দেখা যাবে। কারণ, প্রবাসী ভোটের কেবল অধিকার নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়; এর বিশুদ্ধতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইসিই ইতিমধ্যে জানিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভোট কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রথম ধাপে দূতাবাসভিত্তিক বুথে ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভোটাররা আগেই অনলাইনে নিবন্ধন করবেন, এরপর নির্ধারিত দিনে পাসপোর্ট ও এনআইডি যাচাই করে ভোট দিতে পারবেন।
তবে বিদেশি সরকারের অনুমোদন, নিরাপত্তা প্রটোকল ও সার্ভার স্থাপনা নিয়ে এখনো বিস্তারিত ঘোষণা হয়নি। এটি সময়সীমার দিক থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
এখানে উল্লেখ্য, সৌদি আরবে প্রায় ২৫ লাখ, মালয়েশিয়াতে প্রায় ১২ লাখ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১০ লাখ ও যুক্তরাজ্যে প্রায় পাঁচ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। যেখানে ডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণা, সেখানে এত কম সময়ে এত মানুষের ভোট কীভাবে নিশ্চিত করবে?
বাংলাদেশিরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, জীবিকার তাগিদে কিংবা উন্নত জীবনের সন্ধানে। প্রবাসে থেকেও দেশের রাজনীতি ও ভাগ্য নির্ধারণে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের প্রবাসীরা যে দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তা জুলাই অভ্যুত্থান দেখিয়েছে।
তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। তাঁদের অবশ্যই ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভোটের যে চিত্র আমরা দেখি, তা উৎসাহব্যঞ্জক হলেও তাতে লুকিয়ে আছে বহু ফাঁকফোকর। এটি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।
প্রবাসী ভোটদানের প্রথম ধাপ হলো নিবন্ধন। আর এই ধাপেই হোঁচট খায় অনেক দেশ। পাসপোর্ট, এনআইডি ও জন্মসনদ তিনটি আলাদা সিস্টেমে ছড়িয়ে থাকায় ডুপ্লিকেশন এবং যাচাই সমস্যাই সবচেয়ে বড় বাধা।
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৩ কোটি এনআইডি ইস্যু হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবাসী অবস্থান বা বিদেশে বসবাসের অবস্থা ট্র্যাক করার কোনো আপডেটেড ডেটাবেজ নেই। ভারতে নিবন্ধিত ১ দশমিক ২ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে মাত্র ২ হাজার ৯৫৮ জন ভোট দিয়েছিলেন।
কারণ, ভোট দিতে হলে দেশে ফিরতে হয়, অনলাইন বা দূতাবাসভিত্তিক ব্যবস্থা নেই। ফিলিপাইনসেও ১০ মিলিয়নের বেশি প্রবাসীর মধ্যে ১৫ শতাংশের কম নিবন্ধন করেন এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ প্রবাসী ভোট দেন। অর্থাৎ মোট প্রবাসীর ৩-৪ শতাংশ ভোট দেন। প্রবাসীরা সেখানে ব্যস্ত; ভোটব্যবস্থা দূরের; আর অনেকে মনে করেন, তাঁদের ভোটে কিছু পরিবর্তন আসে না।
যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও ভোটারকে প্রতিবছর স্থানীয় নির্বাচন অফিসে ফেডারেল পোস্ট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হয়। এই প্রক্রিয়া প্রবাসী ভোটারদের জন্য সময়সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর হতে পারে।
বাংলাদেশের কোটি প্রবাসী নাগরিকের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করা এবং তাঁদের প্রতিবছর বা প্রতিবার নির্বাচনের আগে আবার নিবন্ধনের মতো কঠোরতা আরোপ করা হলে ভোটের হার খুব বেশি হবে না।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভোটের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা। শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনসের বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে সতর্ক করেছেন, একই ঠিকানায় অনেক প্রবাসী ভোটার থাকলে ভোট কিনে নেওয়া, জোর করে প্রভাবিত করা বা কূটনৈতিক মিশনে রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে শ্রমিকেরা স্পনসর বা ‘কাফালা’ সিস্টেমের আওতায় থাকেন, সেখানে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা আরও কঠিন হবে।যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ভোটদান একটি ফেডারেল অপরাধ ও এর জন্য সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
অবৈধ ভোটদানে সহায়তাও এখানে একটি ফেডারেল অপরাধ, এমনকি অনেক স্টেটে অন্যকে বৈধ পোস্টাল ভোট দেওয়াতে সহায়তায়ও অপরাধ। কারণ, মনে করা হয় এর মাধ্যমে মানসিকভাবে দুর্বল লোকদের ভোট একপক্ষে নিয়ে আসা যাবে।
এই অপরাধকে বলা হয় ‘ব্যালট হার্ভেস্টিং’। ভোট জালিয়াতি রোধে এ ধরনের কঠোর আইনি পদক্ষেপ ও একটি ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের’ ব্যবস্থা অপরিহার্য। ভোটের ফলাফল নিয়ে কোনো ধরনের প্রভাব বা দুর্নীতির অভিযোগ এলে তা পুরো নির্বাচনপ্রক্রিয়ার ওপরই মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে।
বাংলাদেশে এখনো প্রবাসী ভোট–সংক্রান্ত স্পষ্ট আইন প্রণয়ন হয়নি। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটাধিকার নাগরিকত্ব নির্ভর হলেও বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের আইনি অবস্থান স্পষ্ট নয়। তাই ‘প্রবাসী ভোট আইন ২০২৫’ নামে একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যেখানে ভুয়া নিবন্ধন বা অনৈতিক প্রভাবের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান থাকবে।
প্রবাসী ভোট গ্রহণে কোন পদ্ধতি নেওয়া হবে, তা একটি বড় প্রশ্ন। উন্নত দেশগুলো ও আমাদের প্রতিবেশী গণতন্ত্রগুলো কীভাবে প্রবাসী ভোট তত্ত্বাবধান করছে, তা আমাদের দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।
দূতাবাস/কনস্যুলেটে ভোট : যুক্তরাজ্যে প্রবাসী কমিউনিটির বেশির ভাগই দূতাবাস ও কনস্যুলেটে সরাসরি ভোট দেওয়ার পক্ষে মত দেন। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। আমাদের প্রবাসীদের জন্যও এই ব্যবস্থা ভালো হতে পারে।
ব্যালট/অনলাইন ভোটিং : পোস্টাল বা অনলাইন ব্যালটে ভোটদানের সুযোগ থাকলেও এর সুরক্ষা ও বিশ্বাসযোগ্যতা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।
শুধু নিবন্ধনই নয়, নিবন্ধনের পর ভোটারদের কাছে নির্বাচনের সময়মতো ব্যালট পৌঁছানোও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আবার সমস্যা দেখা যায়, যখন ব্যালট চ্যালেঞ্জ করা হয়, যেমন পেনসিলভানিয়ায় ৪ হাজারের বেশি প্রবাসী ভোটারের ব্যালট প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল।
উন্নত দেশগুলোয় ও অনলাইন ব্যালট পুরোপুরি নিখুঁত হয়নি। বাংলাদেশে যদি দুর্বল সার্ভার বা তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা হুমকিতে পড়বে।
স্বচ্ছ রেজিস্ট্রেশন ও ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া : যুক্তরাজ্যের মতো কঠোর যাচাই ও বছরে একবার নবায়নের নিয়ম থাকা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ফেডারেল পোস্ট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম কাজ করে, ভারতে ফরম ৬ এ-এর অনলাইন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশকেও অবশ্যই একটি সহজ, অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন ও ভোটিং প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যেখানে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়।
নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান : প্রবাসী ভোটিং প্রক্রিয়া তদারকির জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা।
সচেতনতা বৃদ্ধি: প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রবাসী ভোটদান প্রকল্পকে সফল করতে হলে কেবল আইন পাস করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের এমন একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যেখানে ভোটারদের যোগ্যতা নির্ধারণ, নিবন্ধনপদ্ধতি এবং ভোট গণনাপদ্ধতির একটি স্পষ্ট কাঠামো থাকবে।
ভারতের ‘বাধামূলক’ নীতির মতো জটিলতা পরিহার করে তুরস্ক বা ডোমিনিকান রিপাবলিকের মতো ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ নীতি অনুসরণ করতে হবে (তাদের প্রবাসীদের জন্য সরাসরি সংসদীয় আসন সংরক্ষিত)।
এ তো গেল দেশের বাইরের সমস্যা। দেশে কি সমস্যা হচ্ছে না? যাঁরা বিদেশে রেজিস্ট্রেশন করবেন, দেশে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, এই প্রশ্নেরও এখনো কোনো উত্তর নেই।
এই কাজ যদি না করা হয়, তাহলে এই ভোটগুলো দিয়ে কারচুপি হওয়ার সুযোগ থাকে। এরই মধ্যে একটি রাজনৈতিক দল ঘরে ঘরে গিয়ে কারা কারা নির্দিষ্ট ঠিকানায় নেই, তার তালিকা করছে। এটা দুভাবে কাজে লাগানো হতে পারে: জাল ভোট ঠেকাতে অথবা জাল ভোট দিতে। আমাদের তাই সতর্ক থাকা উচিত।
এ ছাড়া দেশের অনেকে বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু দেশে তাঁদের ভোটার নম্বর আছে। তাদের ব্যাপারে কি কোনো সিদ্ধান্ত আছে? এ ছাড়া সবচেয়ে বড় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা হলো, বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনী আইন বা প্রতীক চিহ্নিত ব্যালট পেপার ভোটিং সিস্টেম প্রবাসী ভোটের জন্য উপযোগী নয়।
বিদেশে অবস্থানকারী একজন ভোটার কীভাবে তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীকে চিনবেন এবং ভোট দেবেন, তার কোনো স্পষ্ট পদ্ধতি এখনো চিন্তা করা হয়নি। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ (১৩ মিলিয়ন)। রেমিট্যান্স প্রেরণের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ।
২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৭ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। তাই ভোট কেবল তাঁদের একটি অধিকার নয়, এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি প্রবাসীদের আস্থা ও অংশগ্রহণের প্রতীক।
তাই তাড়াহুড়ো না করে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, সুচিন্তিত, নিরাপদ ও স্বচ্ছ একটি প্রক্রিয়া তৈরি করাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত।শ্রীলঙ্কার বিশ্লেষক হেট্টিয়ারাচ্চি যেমন বলেছিলেন, ‘একটি খারাপ প্রক্রিয়া ভালো ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে।’
অন্যথায় এই সৎ উদ্যোগটিই ভুল বাস্তবায়নের কারণে রাজনৈতিক অবিশ্বাস ও বিভাজনের উৎস হয়ে দেশের জন্য এক ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সুবাইল বিন আলম ও সফিকুর রহমান দুজনই নাগরিক কোয়ালিশন ও বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের সদস্য। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে